বিশ্লেষণ
বাংলাদেশ কি ‘বিশ্ববিদ্যালয়বাজি’র খেসারত দিচ্ছে
বাংলাদেশের বর্তমান উচ্চশিক্ষার যে নীতি ও ধারা, তাতে ‘যত বিশ্ববিদ্যালয় তত উচ্চশিক্ষা’ নামে একটি অদৃশ্য স্লোগান রচিত হয়েছে। ফলে একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় বানানো হচ্ছে। এই কৌশল কি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আদৌ কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে? এই লেখায় সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন সৌমিত জয়দ্বীপ
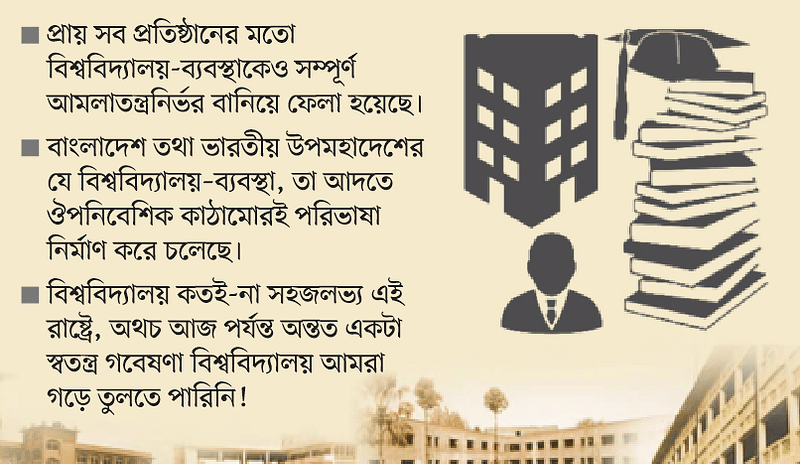
বাংলা ভাষায় ‘বাজ’যুক্ত বহু নেতিবাচক বিশেষণের জমায়েত ঘটেছে। যেমন চাঁদাবাজ, তোলাবাজ, মামলাবাজ, চালবাজ, রংবাজ, ফন্দিবাজ, ধড়িবাজ ইত্যাদি। এই ধারাবাহিকতায় নতুন সংযোজন হতে পারে ‘শিক্ষাবাজ’ শব্দটি। শিক্ষার মতোই শিক্ষাবাজেরও নানা ধারা-উপধারা থাকতে পারে; উল্লেখযোগ্য হলো ‘বিশ্ববিদ্যালয়বাজ’, বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে রূপান্তরের সূত্রানুসারে ‘বিশ্ববিদ্যালয়বাজি’।
আজকের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গায়ে মধ্যবিত্তের উত্তরোত্তর উন্নয়ন গল্পের যেন প্রতীক হয়ে উঠেছে এই ‘বিশ্ববিদ্যালয়বাজি’। রাষ্ট্রের উদ্বাহু ‘সদিচ্ছা’ আর মধ্যবিত্তের ‘উচ্চশিক্ষাঙ্ক্ষা’র (উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা) এমন চমৎকার মণিকাঞ্চনযোগ প্রায়-অভূতপূর্ব!
এই মণিকাঞ্চন যোগময় অবাস্তবিক বিশ্ববিদ্যালয়বাজির কাফফারা দিচ্ছে আজকের বাংলাদেশ। উন্নয়নবাদের তুমুল প্রচার শেষ পর্যন্ত ‘অতি প্রয়োজনীয়তা’র যে নিশান তুলে ধরেছে, তাতে আস্ত বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থাটিরই কবর রচনা হয়ে গেছে এই রাষ্ট্রে।
আর এই কবর রচনার মূল কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থাকে যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার মধ্য দিয়ে বুঝতে না চাওয়ার মন ও মনন। ফলে প্রায় সব প্রতিষ্ঠানের মতো বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থাকেও সম্পূর্ণ আমলাতন্ত্রনির্ভর বানিয়ে ফেলা হয়েছে এবং এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যবস্থার প্রাচুর্য ও সম্ভাবনাকে নাকচ করে কেবল উন্নয়নবাদী বয়ানের রাজনীতি করা হয়েছে।
২.
এ কথা সত্য, বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের যে বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থা, তা আদতে ঔপনিবেশিক কাঠামোরই পরিভাষা নির্মাণ করে চলেছে। ঔপনিবেশিক এই কাঠামোকে প্রায় মহিরুহে পরিণত করে গিয়েছিলেন লর্ড কার্জন।
কিন্তু ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের কারণে কার্জনের নাম যতটা উচ্চারিত হয়, ততটা উচ্চারিত হয় না ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়-কাঠামো পুনর্গঠনের কারণে। কার্জন শেষতক ম্যাকলে স্কুলের ‘ভাগ কর, শাসন কর’ নীতিরই পথানুসারী, চার্লস উডেরই মতানুসারী।
১৮৫৪ সালে উডের ডিসপ্যাচে তিনটি প্রেসিডেন্সি টাউনে (কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ) তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হলেও আদতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তিনটি বন্দর নগরীতে। প্রকাশ্যে বলা হয়নি, কিন্তু বন্দরকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল বিদ্যামনকে বণিক-মননে রূপান্তর করার প্রকল্প হিসেবে। কার্জন সেই রূপান্তরকে বরং আরও এগিয়ে নিতে ঔপনিবেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থার খোল নলচে বদলের ভান করেছেন।
১৯০২ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন এবং এই কমিশনের সুপারিশে ১৯০৪ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করে কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও বেশি সরকারনিয়ন্ত্রিত ও আমলাতান্ত্রিক বানিয়েছেন।
ঔপনিবেশিক শাসকেরা এই প্রতিষ্ঠা প্রকল্পকে তাদের উন্নয়নবাদী রাজনীতির গৌরবগাথা হিসেবে প্রচার করে গেছেন বরাবর। কিন্তু ঔপনিবেশিক মননের অন্দরের কথাটা বলে ফেলেছিলেন লর্ড রিপন, ১৯২৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে। তিনি বলেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলো বঙ্গভঙ্গ রদের ‘চমৎকার রাজকীয় ক্ষতিপূরণ’(স্প্লেন্ডিড এম্পেরিক্যাল কমপেনসেশন)।
এই নিয়ন্ত্রণপদ্ধতির পরে সমালোচনা করা হয়েছিল ১৯১৯ সালে প্রকাশিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বা স্যাডলার কমিশনের প্রতিবেদনে। তবু পরবর্তী সময়ে কার্জনের নীতি অনুসরণ করেই ভারতবর্ষে বিভিন্ন অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছে। ফলে ১৮৫৭-১৮৮৭ পর্যন্ত ৩০ বছরে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র পাঁচটি হলেও কার্জনের রোগে পেয়ে ১৯১৬-১৯৪৭ পর্যন্ত ৩১ বছরে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ১৭টি।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রকল্প হিসেবে কী লজ্জাজনক এ বয়ান। কিন্তু কোনোকালে এ নিয়ে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়নি আমাদের। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পক্ষে ছিলেন নাকি বিপক্ষে, তা নিয়ে এখনো কত তর্ক-বিতর্ক। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন ও বিশ্ববিদ্যালয়-দর্শনকে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বোঝাপড়া করলে, পক্ষে-বিপক্ষের এই দুই গ্রুপই তাত্ত্বিকভাবে অপাঙ্ক্তেয় হয়ে পড়বে।
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন মূলত প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার প্রকল্পে, যা আদতে ভারতবর্ষের আদি ও বিঔপনিবেশিক তপোবনীয় ও গুরুকুলীয় বিশ্ববিদ্যালয়-দর্শনেরই প্রতিনিধিত্ব করে। সেই দর্শনটি আমরা বুঝতে পারিনি কিংবা বুঝেও অবহেলা করেছি বলেই, আমাদের শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থার আজও এই ঔপনিবেশিক দশা।
৩.
বাংলাদেশের বর্তমান উচ্চশিক্ষার যে নীতি ও ধারা, তাতে ‘যত বিশ্ববিদ্যালয়, তত উচ্চশিক্ষা’ নামে একটি অদৃশ্য স্লোগান রচিত হয়েছে। ফলে ‘বিশ্ববিদ্যালয়বাজি’র এক করুণ ব্যবসায় লিপ্ত হয়েছে আমাদের রাষ্ট্র। জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় করার একধরনের ‘কার্জনিয়ান ডিজিজ’ ধরেছে এই রাষ্ট্র ও নীতিনির্ধারকদের। একে তারা ‘উন্নয়নের মহাসড়কের এক জাজ্বল্যমান গল্প’ হিসেবে প্রচারে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এই গল্পের একটি প্রতি গল্প হলো ‘নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, তবু ভূমিহীন, গৃহহীন’ শীর্ষক প্রতিবেদনটি (প্রথম আলো, ৮ মে ২০২৪)।
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন প্রতিষ্ঠিত ১৮টি পাবলিক বা সর্বজন বা বারোয়ারি (পাবলিকের অনূদিত-প্রতিশব্দ হিসেবে ‘বারোয়ারি’ ব্যবহার করা হলো) বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমি নেই। সেগুলো পরিচালিত হচ্ছে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের ভবনে কিংবা ব্যক্তিমালিকানাধীন ভবন ভাড়া করে। ফলে চরমভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে এই নবাগত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম।
পরিতাপ হলো, শিক্ষা কার্যক্রম ঠিকঠাক না চললে হাহাকার যতটা হবে, এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা স্নাতক-স্নাতকোত্তর হয়ে বের হয়েও যে বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক বিদ্যাচর্চার প্রকৃত দর্শনের সান্নিধ্য পাবেন না, তা নিয়ে কেউ একটা কথাও খরচ করবেন না! কেননা সে দর্শনটি সম্বন্ধে আমরা জনপরিসরে ওয়াকিবহালই নই। বিশ্ববিদ্যালয় মানে আমরা বুঝি, গণহারে চাকুরে তথা ‘করণিক’ বা ‘কেরানি’ তৈরি করার একটি যন্ত্র, যার চাবিটি চলমান বাজারব্যবস্থার কাছে বন্ধক দেওয়া আছে!
আপত্তি ও সমালোচনার পরিধি তাই শুধু ‘অস্থায়ী ক্যাম্পাস’ নিয়ে চলমান এই ১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের করুণ দশায় সীমিত রাখলে চলে না। যখন পুরো ব্যবস্থাটাই ধসে পড়ছে, যখন নগর পুড়ে গেছে, তখন দেবালয়ও টিকবে না৷ স্বীকার করতে হবে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বড়জোর চলছে কলেজ বা মহাবিদ্যালয়ের মতো; কিন্তু, শুনতে আভিজাত্যপূর্ণ লাগে বলে, এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রপঞ্চটি।
স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংসদে পাসকালে যে দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল চারটি, বিশেষায়িত বুয়েট ও বাকৃবি মিলে মোট ছয়টি। সেই দেশের ৫০ বছরের ইতিহাসে ইউজিসির তথ্যানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ১৬৯টি। এটাই হলো বিশ্ববিদ্যালয়বাজি! এর মধ্যে সর্বজন বা বারোয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় ৫৫টি, বেসরকারি ১১৪টি।
ভয়ানক ব্যাপার হলো, বিশ্ববিদ্যালয়বাজির চূড়ান্ত মাত্রা দেখিয়ে ২০১৩ সালের পর বারোয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ২০টি এবং অনুমোদন হয়েছে আরও ৬টির, যেগুলোর অধিকাংশই বিশেষায়িত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কৃষি, চিকিৎসা বা ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ বিশেষায়িত এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কত অনায়াসেই না কলেজিয়েট তকমায় পরিচালনা করা যেত বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিভুক্ত করে। তাতে শিক্ষার্থীদের সনদের ওজনও একটু ‘ভারী’ হতো।
এ দেশের জনশক্তিকে পুঁজিবাজারে কাজে লাগানোর জন্য দরকার ছিল প্রাইমারি থেকে টারশিয়ারি পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর। প্রয়োজন ছিল যথাসম্ভব মানসম্পন্ন বিশেষায়িত কলেজিয়েট কারিগরি শিক্ষার।
যে দেশে বড়জোর বিভাগীয় শহরগুলোর প্রতিটিতে একটি ও সারা দেশে একটি করে বিশেষায়িত (কৃষি, প্রযুক্তি ও চিকিৎসা) বিশ্ববিদ্যালয় হতে পারত; আর অন্যগুলোর মর্যাদা হতে পারত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মহাবিদ্যালয়। সেই দেশে কি না আমরা ঝুঁকে গেলাম জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিশ্ববিদ্যালয়বাজিতে।
বিশ্ববিদ্যালয় কতই-না সহজলভ্য এই রাষ্ট্রে! অথচ আজ পর্যন্ত অন্তত একটা স্বতন্ত্র গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় আমরা গড়ে তুলতে পারিনি, যেটি হতো প্রকৃতার্থে আমাদের ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়’। গবেষণা-মনন দিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিনি, এককালে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশরাও তা করেনি। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মনন হলো কেরানি বানানোর মনন; ফলে গবেষক তৈরির কথা প্রায় কেউই ভাবেননি।
‘বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রপঞ্চটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, মেকলে,উড বা কার্জনের নীতিকেই আমরা সসম্মানে বহাল রেখেছি, যত পার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত করণিক বানাও, যাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বৃত্তির পুরোটাই শাসকশ্রেণির মনোরঞ্জনে খরচ হবে।
৪.
এ পর্যন্ত যা বলা হলো, তার প্রমাণ ও প্রতিফলন পাওয়া যায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ফি বছরের বৈশ্বিক র্যাঙ্কিংয়ে। পৃথিবীতে বৈশ্বিক বিশ্ববিদ্যালয়-র্যাঙ্কিং করা বড় বড় প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা জানি, এর মধ্যে দ্য টাইমস হায়ার এডুকেশন, কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডস এবং একাডেমিক র্যাঙ্কিং অব ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিজ তথা সাংহাই র্যাঙ্কিং অন্যতম।
টাইমস হায়ার এডুকেশন তাদের নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয় র্যাঙ্কিংয়ের বাইরেও, ‘নবীন বিশ্ববিদ্যালয় র্যাঙ্কিং’ নামে আরেকটি র্যাঙ্কিং করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বয়স হতে হয় সাধারণত অনূর্ধ্ব ৫০ বছর। বয়সভিত্তিক এই র্যাঙ্কিংয়ে ২০২৪ সালে বাংলাদেশের মধ্যে প্রথম হয়েছে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় (৩০১-৩৫০) ও দ্বিতীয় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় (৩৫১-৪০০)। তৃতীয় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (৪০১-৫০০) ও চতুর্থ সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫০১-৬০০)।
নবীন-প্রবীণের ক্যাটাগরির বাইরে গিয়েও ব্র্যাক ও নর্থ সাউথের মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছরই বাংলাদেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে থাকছে। অথচ জনগণের অর্থে উন্নয়নের মহাসড়কে নাম লেখানো বারোয়ারি প্রান্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোনো তালুক সন্ধান করা যাচ্ছে না। তবু জনগণের টাকায় প্রান্তিক জেলাগুলোয় ‘ভূমিহীন ও গৃহহীন বিশ্ববিদ্যালয়’ স্থাপনের কাজ মহাসমারোহে এগিয়ে চলেছে। উল্টো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থায়ী ক্যাম্পাসে যেতে কতটা বাধ্য, সেটা বারবার আইনের দোহাই দিয়ে মনে করিয়ে দেওয়া হয়।
‘ভূমিহীন, গৃহহীন’ বারোয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে আশ্চর্যজনকভাবে ইউজিসির তরফে কোনো হেলদোল কিংবা আইন নেই। স্থায়ী ক্যাম্পাস সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই জরুরি। তাহলে একযাত্রায় দুই ফলের এমন যুক্তিহীন দৃষ্টান্ত কেন থাকবে! বরং রাষ্ট্র ও সরকার পারত শিক্ষা-গবেষণায় এগিয়ে থাকা কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্তত ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে কম মূল্যে স্থায়ী ক্যাম্পাস নির্মাণে সহায়তা করতে।
এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যে রাষ্ট্রের নাগরিক সন্তানেরা পড়েন, বিবেচনাটি তো অন্তত থাকতে পারত। কিন্তু কর্তাদের সব উন্নয়নের আলো গিয়ে পড়েছে জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চতুর বিজ্ঞাপনে। এ উন্নয়ন কতটা আত্মিক আর কতটা আর্থিক স্বার্থে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।
৫.
এ কথা সত্য, ঔপনিবেশিকতার ঔরসে জন্ম হলেও প্রতি-ঔপনিবেশিক জাতীয়তাবাদী ভূমিকার কারণে বাংলাদেশকে তার বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থাই এতে দূর এনেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক-চেতনার আঁতুড়ঘরে জন্ম নিয়েছে বাংলাদেশ। কিন্তু, পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর দশকের সে সময়ের সঙ্গে আজ আর বাস্তবিক কারণেই তুলনা করা চলে না।
রাষ্ট্র-সমাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যাপীঠ তাত্ত্বিকভাবেই এখন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কাজ বা ফাংশন করছে না বাংলাদেশে। মানহীন ও পদোন্নতিনির্ভর গবেষণা, ছাত্রসংসদহীন ক্যাম্পাসে দলীয়করণ ও সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতি, শিক্ষা কার্যক্রমের যাচ্ছেতাই দশাসহ সরকারি চাকুরিকেন্দ্রিক পড়ালেখার প্রতি শিক্ষার্থীদের নিদারুণ ঝোঁক পুরো ব্যবস্থাটাকেই ঝুঁকিতে ফেলেছে।
নীতিনির্ধারকেরা স্বীকার করতে না চাইলেও দেখা যাবে, সামগ্রিক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ব্যবস্থাটি মৃতপ্রায় ও অকার্যকর। আর একে আরও বেশি ত্বরান্বিত করেছে অপ্রয়োজনীয় ও অপরিকল্পিত বিশ্ববিদ্যালয় ও করণিক সৃষ্টির ‘রাজকীয়’ বিশ্ববিদ্যালয়বাজি।
এ রকম অবস্থায় হরে-দরে কেরানি উৎপাদনের উন্নয়নবাদী বিদ্যা-ব্যবসায়ী ঔপনিবেশিক-সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে যত দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষক সৃষ্টির মূলমন্ত্রে ফিরিয়ে আনা যাবে, তত দ্রুত বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ব্যবস্থা ফসিল দশা থেকে মুক্তি পাবে। তা না হলে বিশ্ববিদ্যালয়বাজির কাফফারা পুরো রাষ্ট্রকে এখন যেমন দিতে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও দিতে হবে।
●ড. সৌমিত জয়দ্বীপ সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়