পারমাণবিক পাকিস্তানের রূপকার আবদুল কাদির খান: আলাপচারিতা
পাকিস্তানের পারমাণবিক বোমার জনক আবদুল কাদির খান আর নেই। গতকাল রোববার সকালে ইসলামাবাদের একটি হাসপাতালে তিনি মারা যান। পাকিস্তানকে বিশ্বের প্রথম পরমাণু শক্তিধর মুসলিম দেশ বানানোর কৃতিত্ব আবদুল কাদির খানের। নিজ দেশে তিনি জাতীয় বীর হিসেবে নন্দিত। বিশিষ্ট কলাম লেখক, আন্তর্জাতিক বিষয়াদির বিশ্লেষক এবং বাংলাদেশ সরকারের সাবেক পররাষ্ট্রসচিব প্রয়াত ফারুক চৌধুরীর লেখা ‘পারমাণবিক পাকিস্তানের রূপকার আবদুল কাদির খান: আলাপচারিতা’ প্রথম আলোর পাঠকদের জন্য পুনঃপ্রকাশিত হলো।
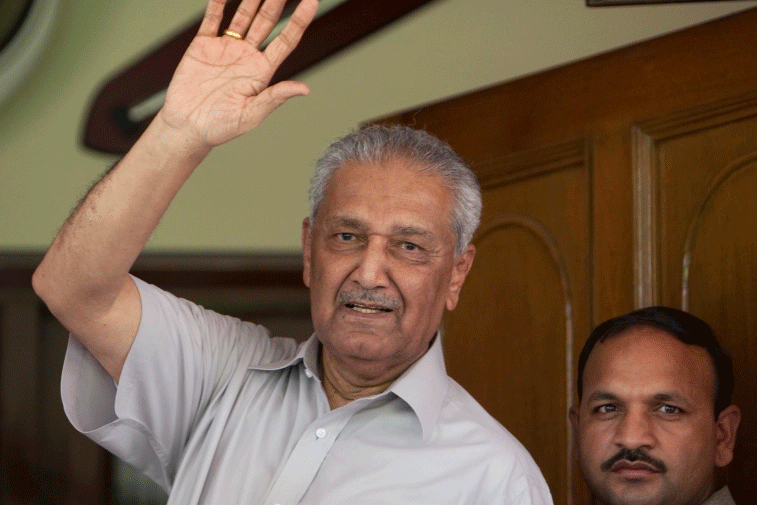
সুদীর্ঘ কর্মজীবনের গঠনাত্মক বেশ কিছু সময় আমার করাচি আর ইসলামাবাদে কেটেছে। তাই পাকিস্তান আমার কাছে পরিচিত মানুষ আর বন্ধুবান্ধবের দেশ। বহু স্মৃতিবিজড়িত, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যময়, ঐতিহাসিক সেই ভূখণ্ডটিতে কাটিয়ে এসেছি এই ১৯৯৯ সালের মার্চ আর এপ্রিলে আনন্দদায়ক তিনটি সপ্তাহ। পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সান্নিধ্যে উষ্ণ আতিথেয়তা লাভ করেছি, পরিচিত হয়েছি বিশেষ করে সেই দেশের নতুন প্রজন্মের অনেক নবীনের সঙ্গে, স্মরণীয় সেই তিনটি সপ্তাহে।
বর্তমান পাকিস্তানের সমাজ বিবাদ-বিসংবাদে জর্জরিত। এই বিরোধ আর অনৈক্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষাকেন্দ্রিক, ধর্মীয় ও গোত্রীয়, তার পরিব্যাপ্তি আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আর তা প্রায়শই ভয়াবহ আকার ধারণ করে সহিংস রক্তক্ষয়ী সংঘাত আর সংঘর্ষে; সংকীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা আর ক্ষোভের চরম বেদনাদায়ক বহিঃপ্রকাশে। তিন সপ্তাহে আমি ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি ছাড়া লাহোর, পেশোয়ার, সোয়াত, খাইবার, মালাকান্দ আর করাচি সফর করেছি। লেখকের কল্পনায় আলেকজান্ডার কথিত ‘কী বিচিত্র এই দেশে’ মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় উপলব্ধি করেছি, এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দেশের সমস্যাবলি সম্পর্কে অনুভূতি আর মতামতের বিস্তর প্রভেদ রয়েছে। কিছু প্রশ্ন, কিছু জিজ্ঞাসা আর বিতর্কের জের টানলেই পাকিস্তানির আবরণ থেকে আত্মপ্রকাশ করে কোনো না কোনো উপজাতীয় রূপ-পাঞ্জাবি, পাখতুন, সারাইকি, সিন্ধি, বেলুচি অথবা মোহাজের-রাষ্ট্রভাষা উর্দুর সেই দেশেও যাদের ‘উর্দুভাষী’ বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। ধর্মীয় বলয়ে ইসলামি সেই রাষ্ট্রে তারা বিদ্যমান সুন্নি আর শিয়া অথবা ভীতসন্ত্রস্ত কাদিয়ানি আর খ্িরষ্টান। সিন্ধু আর সীমান্ত প্রদেশে ক্ষুদ্র হিন্দুগোষ্ঠী রয়েছে, পাঞ্জাবে রয়েছে কিছু শিখও। শেষোক্ত দুই সম্প্রদায়ের কারও সঙ্গেই সাক্ষাতের অবকাশ আমার হয়নি এই সফরে।
৮ এপ্রিল অপরাহ্নে গাড়িতে করে ইসলামাবাদ থেকে রাওয়ালপিন্ডির প্রায় পনেরো কিলোমিটার পথ যেতে যেতে মনে ছিল চাপা উত্তেজনা। ভাবছিলাম কী প্রশ্ন তাঁকে করা সমীচীন হবে। রিঅ্যাক্টরে প্লাটিনাম সমৃদ্ধকরণের আলট্রা সেন্ট্রিফিউজ প্রণালি সম্বন্ধে দু-একটি সাধারণ প্রবন্ধ পড়ে কিছু বোঝার ব্যর্থ প্রচেষ্টা অবশ্য নিয়েছিলাম। তাতে এটুকু আমার বোধগম্য হয়েছিল যে আল্ট্রা সেন্ট্রিফিউজ পদ্ধতিটি ভারতে ব্যবহৃত পদ্ধতির চেয়ে নাকি আধুনিকতর। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করার জ্ঞান আমার নেই। দ্বিতীয়ত ড. এ কিউ খান বৈজ্ঞানিক হিসেবে পাকিস্তানের পারমাণবিকায়নে তাঁকে প্রদত্ত জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার পারমাণবিকায়ন সম্বন্ধে কোনো বিস্তারিত রাজনৈতিক আলোচনার সূত্রপাত করা হবে অপ্রাসঙ্গিক। অতএব গাড়িতে বসেই সিদ্ধান্ত নিলাম যে সার্থক এই বৈজ্ঞানিকের ভেতরের মানুষটিকেই আমার কথোপকথনের মধ্যে জানার চেষ্টা করব।
ড. আবদুল কাদির খানের অফিসের দোরগোড়ায় আমার গাড়ি ভিড়তেই আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন তাঁর একান্ত সচিব মেজর ইসলাম। পরিচয়ের আনুষ্ঠানিকতার পর তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন দেয়ালে কাঠের প্যানেল করা একটি ওয়েটিং রুমে। ধূসর রঙের কাপড়ের একটি সোফাসেট রয়েছে সেই কামরায় আর সোফার ফ্রেমের কাঠের বাদামি রং ম্যাচ করছে দেয়ালের প্যানেলের রঙের সঙ্গে। দেয়ালে টাঙানো বেশ কটি ছবি ড. আবদুল কাদির খানের সঙ্গে দেশি-বিদেশি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের। আর রয়েছে পাকিস্তানের ১৯৯৮ সালের ২৮ মে পারমাণবিক বিস্ফোরণের গোটা দুয়েক আর ১৯৯৮ সালের ৬ এপ্রিল নিক্ষিপ্ত ঘোরি-১ মিসাইলের একটি বড় আকারে রঙিন ছবি। মিনিট পনেরো অপেক্ষার পর পাশের দরজাটি খুলে গেল। প্রবিষ্ট হলাম মেজর ইসলামের সঙ্গে ড. আবদুল কাদির খানের নাতিবৃহৎ অফিস কামরায়। বেশ বড় একটি কাঠের অফিস-টেবিলের পেছনে বসা ড. খান উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলটি ঘুরে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন উষ্ণ করমর্দনে। লম্বা তিনি ছয় ফুটেরও বেশি, সুঠাম চেহারা, মাথায় কাঁচা-পাকা ব্যাকব্রাশ করা চুলের তিন-চতুর্থাংশই পাকা, যত্নে কাটা কাঁচা-পাকা গোঁফ, পরনে গাঢ় নীল রঙের হাফ স্লিভ সাফারি স্যুট, বাঁ দিকের বুকপকেটে একটি ফাউন্টেন পেন, চোখেমুখে পরিতৃপ্তির ছাপ। না, চুল উষ্কখুষ্ক, আপনভোলা প্রফেসর তিনি মোটেই নন। বরং দেখে মনে হয়, কোনো এক সার্থক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অবসরপ্রাপ্ত, সুবেশী, সুদর্শন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ভাবতে অবাক লাগল, সামনে দাঁড়ানো স্মিতহাস্য এই মানুষটি এক বছরেরও কম সময় আগে বেলুচিস্তানের চাখাই পাহাড়ে এমন একটি পারমাণবিক বিস্ফোরণমালা ঘটিয়েছেন, যার প্রতিটি বোমা হিরোশিমার বোমা থেকে ৮০ গুণ বেশি শক্তিশালী, যা পারমাণবিক যুদ্ধ শুরুর পাঁচ মিনিটের মধ্যে কেন্দ্রীয় দিল্লির সাত বর্গকিলোমিটারের পরিধিতে বসবাসকারী নয় লাখ মানুষের প্রাণহানি ঘটাতে পারে। আর যদি কোনো কারণে তাতে বিলম্ব ঘটে, যদি ভারতের ‘অগ্নি’ মিসাইল পোখরানের একটি বোমা মুখে নিয়ে উড়ে আসে রাওয়ালপিন্ডির আকাশে, তাহলে ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি, মারগাল্লা পাহাড়ের শ্যামলিমার ফায়সাল মসজিদ, চার লেনের নাকবরাবর রাওয়ালপিন্ডি-ইসলামাবাদ মোটরপথ আর তার চারপাশে বসবাসকারী কোনো প্রাণীর-তা মানুষ হোক অথবা পশুপাখি-অস্তিত্বই থাকবে না। শুধু তা-ই নয়, পারমাণবিক বোমা মুখে দু-চারটি ‘অগ্নি’ মিসাইল নিমেষেই বিলুপ্ত করে দিতে পারে রাওয়ালপিন্ডি-ইসলামাবাদের অদূরের গান্ধারা সভ্যতার নিদর্শন, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বিম্বিসার, অশোক আর কনিষ্কের পীঠস্থান তক্ষশিলা, যা রামায়ণের সূত্রমতে স্থাপন করেছিলেন শ্রীরামের ভাগিনেয়, ভরতসন্তান তক্ষ, আর যেখানে মহাভারতের কথায়, যুদ্ধজয়ের পর হস্তিনাপুররাজ জনমেজয় সর্প বলিদান উৎসব অনুষ্ঠিত করেছিলেন। ঠিক তেমনি বোমাবাহী দু-চারটি ‘ঘোরি’ মিসাইল, ‘অগ্নি’ মিসাইলের সঙ্গে পারমাণবিক যুদ্ধে যুগপৎভাবে নিমেষেই চিরতরে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে ইব্রাহিম লোদি, নিজামউদ্দিন আউলিয়া, হুমায়ুন, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান আর খাজা মুঈনউদ্দিন চিশতির দিল্লি, আগ্রা আর আজমির তথা ভারতের মুসলিম শাসনের গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী সব স্মৃতিচিহ্ন। এ কোনো বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন নয়, পারমাণবিক সংঘাতে, নিয়মিত এক চরম পরিহাসেই ‘অগ্নি’ সাধন করবে ভারতের সনাতন সভ্যতার স্মৃতিচিহ্নের ধ্বংসযজ্ঞ, আর ‘ঘোরি’ চিরতরে বিলুপ্ত করবে ভারতের মুসলিম ঐতিহ্যের অপূর্ব সব নিদর্শন। পারমাণবিক সংঘাতে তা-ই সম্ভাব্য বাস্তব।
‘না, তা হবে না’-মৃদু হেসে আশ্বাস দিলেন ড. আবদুল কাদির খান। আরও বললেন, ‘উপমহাদেশে পারমাণবিক ভারসাম্য শান্তিই নিশ্চিত করবে। এই ভারসাম্যই আমাদের রক্ষাকবচ। পাশ্চাত্যে যেমনি রয়েছে গত অর্ধশতাব্দী ধরে।’ ভারতীয় পারমাণবিক বৈজ্ঞানিক ড. আবদুল কালামও হয়তো তাঁর সঙ্গে একমতই হবেন। বৈজ্ঞানিকদের এই আশ্বাস আর উপমহাদেশের রাজনৈতিক কর্ণধারদের সুবুদ্ধিই এখন আমাদের এবং ভাবী প্রজন্মের নিরাপত্তার নিশ্চায়ক!
ভারতীয় ভোপাল রাজ্যে ১৯৩৬ সালের ২৭ এপ্রিল আবদুল কাদির খানের জন্ম। পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনিই কনিষ্ঠতম। আর রয়েছে তাঁর দুই বোন, যাঁদের মধ্যে একজন তাঁর কনিষ্ঠ, যিনি তাঁর অতি প্রিয়। স্কুলশিক্ষক বাবা আবদুল গফুর খান চাকরি থেকে অবসর নেন ১৯৩৫ সালে, আবদুল কাদির খানের জন্মের মাত্র একটি বছর আগে। অতএব শৈশব আর কৈশোরে বাবার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলাভের অবকাশ তাঁর হয়েছিল।
নিজের অফিস-টেবিলের চেয়ারে বসেই তাঁর নিজের সম্বন্ধে কথার সূত্রপাত করলেন ড. আবদুল কাদির খান। অফিস কামরার দেয়ালে কাঠের প্যানেলিং। দেয়ালে বেশ কটি ছবি, যার মধ্যে একটি পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের ছবিও রয়েছে দেয়ালে। আর আছে পৃথিবীর একটি মানচিত্র। উপবিষ্ট ড. আবদুল কাদির খানের পেছনের দেয়ালে রয়েছে পবিত্র কোরআনের আয়াত এবং ‘ইয়া আল্লাহ’ ও ‘ইয়া মোহাম্মদ’ লেখা দুটি ক্যালিগ্রাফ।
‘ঘোরি-১’ মিসাইল (সাক্ষাৎকারটি ছিল ‘ঘোরি-২’ মিসাইল নিক্ষেপণের দিন সাতেক আগে) আর চাঘাই পারমাণবিক বিস্ফোরণের রঙিন ছবিও অফিস কামরাটির দেয়ালে শোভা পাচ্ছে। অফিস-টেবিলটির সামনেই রাখা একটি সোফাসেট, যেখানে আমরা গিয়ে বসলাম সাক্ষাৎকার শুরু হওয়ার বেশ কিছু পরে চা-নাশতা খেতে। চায়ের সঙ্গে এল ফিরনি, কেক আর সুস্বাদু পাকোড়া। আমার প্লেটে তা নিজ হাতে তুলে দিলেন ড. আবদুল কাদির খান। তাঁর অতিথিবাৎসল্যে মনে হলো যেন অফিসে নয়, তাঁর বাড়িতে বসে চা-চক্রে যোগ দিয়েছি।
ড. আবদুল কাদির খান আরও বললেন, অত্যন্ত দয়ালু আর নম্র স্বভাবের মানুষ ছিলেন তাঁর বাবা আবদুল গফুর খান। জোরে কথা বলাও ছিল তাঁর না-পছন্দ। তিনি তাঁর সন্তানকে শিখিয়েছিলেন সকল প্রাণীকে ভালোবাসতে। তাই আজও কাজ শেষে বিকেলে ড. খান ইসলামাবাদের মারগাল্লা পাহাড়ের পাদদেশে, ফায়সাল মসজিদের অনতিদূরে তাঁর বাংলোতে যখন ফিরে যান, গোটা পঞ্চাশেক বানর নেমে আসে পাহাড় থেকে তাঁর হাতে খেতে পাবে বলে। বেশ কটি বিড়াল আর কুকুর রয়েছে তাঁর, সব মিলিয়ে প্রায় গোটা বারো। আর রয়েছে তোতা পাখি-কথা বলে, তবে পারমাণবিক কোনো গোপনীয় কথা নয়! মা জুলেখা বেগম ছিলেন পরহেজগার মহিলা, ফারসি আর উর্দুতে ছিল তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ তিনি পড়তেন এবং সেই অভ্যাস ড. আবদুল কাদির খানেরও রয়েছে। নামাজ তাঁর কদাচিৎ কাজা হয়।
ভোপালের হামিদিয়া স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন ১৯৫২ সালে। সেই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে আল্লামা ইকবাল আর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর প্রভাব ছিল প্রভূত। ম্যাট্রিক পাস করার পরই তাঁর বড় ভাইয়ের ডাকে তিনি চলে যান পাকিস্তানের করাচিতে। ভারত তিনি কেন ছাড়লেন, আমার প্রশ্ন ছিল তাঁর কাছে। তাঁর মতে, ভারতে, বিশেষ করে ভোপালে তাঁর পেশাগত সম্ভাবনা সীমিত ছিল। ভোপালে রয়ে গেলে তিনি হয়তো তাঁর বাবার মতো স্কুলমাস্টারের পেশাই বেছে নিতেন, হয়তোবা সেখানেই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে কাটাতেন নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। মাঝারি মেধার ছাত্র ছিলেন তিনি, তাঁর মা-বাবার এমন কোনো প্রত্যাশা ছিল না যে প্রতিটি পরীক্ষায়ই তাঁকে প্রথম হতে হবে। তাঁরা এতটুকু আশা করতেন যে তিনি একজন স্বাভাবিক মানুষ হয়ে গড়ে উঠুন। অতএব লেখাপড়ার কোনো টেনশন তিনি কখনো অনুভব করেননি। পাকিস্তানে তিনি চলে এলেন ১৯৫২ সালে। তাঁর বাবা রয়ে গেলেন ভোপালেই, যেখানে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন ১৯৫৭ সালে।
করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে তিনি বিএসসি পাস করলেন। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি গোটা দুয়েক বেসরকারি প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ ছিলেন। তারপর তিনি প্রার্থী হলেন সরকারের ইন্সপেক্টর অব ওয়েইটস অ্যান্ড মেজারস ( Inspector of Weights and Measures) পদটির জন্য। প্রায় শ দুয়েক দরখাস্ত পড়েছিল মাত্র দুটি পদের জন্য। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তারই একটি পদে তিনি যোগ দিলেন। সেকেন্ড ক্লাস নন-গেজেটেড চাকরি। মাইনে মাসে ১২৫ টাকা। মন্তব্য করলাম, সেই সময়ে তো পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। আমরা যেমন দিয়েছিলাম। তিনি কেন সেই পরীক্ষায় অংশ নিলেন না? সেই পরীক্ষা দেওয়ার চিন্তাই তাঁর মাথায় আসেনি, বললেন ড. খান। ভালোই তো ছিল তাঁর চাকরিটি। তবে গোল বাধালেন তাঁর ‘বস’, চিফ ইন্সপেক্টর মুসা খান। বোম্বাইয়ের লোক ছিলেন তিনি। তাঁর একটি অভ্যাস ছিল কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ওয়েটস অ্যান্ড মেজারস ইন্সপেক্টর থেকে সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে তিনি তাঁদের কাছে লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ার দাবি করতেন! এটা দুর্নীতিই মনে হতো ড. খানের চোখে। তিনি আর তাঁর বসের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলেন না। ইস্তফা দিলেন চাকরি থেকে। দরখাস্ত পাঠালেন ইউরোপের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংল্যান্ডের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছা তাঁর কোনো দিনই ছিল না। ইংরেজদের প্রতি তাঁর বরাবর কিছুটা অনীহাই ছিল, হয়তোবা তারা ভারতের শাসকগোষ্ঠী ছিল বলে। বার্লিনের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি মেটালার্জিতে ( Metallurgy) বছর দুয়েক ট্রেনিং নিলেন। তারপর ১৯৬৭ সালে হল্যান্ডের ডেলফট টেকনোলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি আর ১৯৭২ সালে বেলজিয়ামের লুভেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করলেন। তবে জীবনে ঘটনাচক্রে অনেক কিছুই হয়ে থাকে। জীবন নেয় অপ্রত্যাশিত মোড়। তাঁর যেমনি হয়েছে। হল্যান্ডে তাঁর লেখাপড়ার প্রধান কারণ হলেন তাঁর স্ত্রী হেনি। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর জন্ম, তাঁর মা-বাবা হল্যান্ডেরই বাসিন্দা। ১৯৬২ সালে হল্যান্ডের দ্য হেগে ভ্রমণকালে পোস্ট অফিসে ড. খানের সঙ্গে হেনির প্রথম দেখা। পাকিস্তানে চিঠি পাঠাতে কত অঙ্কের টিকিটের প্রয়োজন, এই মূল্যবান তথ্যটি কাছে দাঁড়ানো হেনি উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছিলেন পোস্ট অফিসের কিউতে দাঁড়িয়ে ড. খানের সরব জিজ্ঞাসায়।
কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন ড. খান। সেখানেই তাঁদের পরিচয়ের সূত্রপাত। জার্মানিতে ফিরে যাওয়ার আগে হেনির নাম-ঠিকানা লিখে নিতে ভুল হয়নি ড. খানের। ‘হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল’ ড. খানের জার্মানি ছেড়ে দিয়ে হল্যান্ডেই তাই লেখাপড়া। হল্যান্ডের পাকিস্তান দূতাবাসে ১৯৬৪ সালে তাঁদের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন কাকতালীয়ভাবে সেই দূতাবাসে আমারই পূর্বসূরি জামিল উদ্দিন হাসান। ১৯৬৫ সালে আমি হল্যান্ডের পাকিস্তান দূতাবাসে বদলি হই। অতএব, তাঁদের বিয়ে বছরখানেক পরে হলে আমাকেই সেই দায়িত্ব পালন করতে হতো, এই কথাটি ড. খানকে স্মরণ না করিয়ে দিয়ে পারলাম না। যেকোনো স্থানের সমকালীন স্মৃতির একটি বাঁধন রয়েছে। আমার এই উক্তি সেই বাঁধনটিই যেন সৃষ্টি করল।
পাকিস্তানে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ড. আবদুল কাদির খানের বরাবরই ছিল। ১৯৬৭ সালে এমএসসি পাস করার পর তিনি করাচি স্টিল মিলে চাকরির দরখাস্ত করেছিলেন। কিন্তু কারখানায় কাজের অভিজ্ঞতা নেই বলে তাঁর দরখাস্তটি নাকচ হয়ে যায়। তখনই তিনি বেলজিয়ামের লুভেনে ডক্টরেট করার সিদ্ধান্ত নেন। পিএইচডি পাওয়ার পরও তিনি চাকরির জন্য বেশ কিছু দরখাস্ত করেছিলেন পাকিস্তানে। কিন্তু মেলেনি কোনো উত্তর।
অন্যান্য দেশেও তিনি চাকরির দরখাস্ত করেছিলেন। অফার এসেছিল বেশ কটি পাশ্চাত্য দেশ থেকে। সেগুলোর মধ্য থেকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার আণবিক কমিশনের একটি অফার। তিনি ও তাঁর স্ত্রী অস্ট্রেলিয়া যাত্রার প্রস্ত্ততি যখন নিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই হল্যান্ডের এফডিও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চাকরি পেলেন সিনিয়র মেটালারজিস্টের ( Senior Metallurgist)। সেই কোম্পানিটি ছিল ইউরোপের বৃহত্তর আণবিক গবেষণা কেন্দ্র ইউরেনকোর ( URENCO) সঙ্গে জড়িত। ইউরেনকোর আণবিক প্রোগ্রামের উদ্যোক্তা ছিল তিনটি দেশ-যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি আর হল্যান্ড।
সেন্ট্রিফিউজ পদ্ধতিতে সেখানে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ গবেষণা চলছিল। ধাতুসংক্রান্ত বেশ কটি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিল গবেষণাটি। মেটালারজিস্ট হিসেবে ড. খান বেশ কটি সমস্যার সুরাহা করতে সক্ষম হন। তখনই সেন্ট্রিফিউজ পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর স্পষ্ট ধারণা জন্মে।
পাকিস্তানে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলি তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল। তাঁর কথায়, যেহেতু তিনি তখন বেলজিয়ামে, যেখানে সংবাদমাধ্যমের রয়েছে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, ‘টিক্কা খান এবং তাঁর সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত আচরণ’ টেলিভিশনের পর্দায় দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল, সুযোগ হয়েছিল খবরের কাগজের মাধ্যমে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সঠিক অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার। ভারতও তখন খুব সক্রিয় ছিল, বললেন তিনি। টেলিভিশনের পর্দায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ প্রত্যক্ষ করে তিনি গভীর আঘাত পেয়েছিলেন। অথচ দাবি করা হতো, সেই সেনাবাহিনী নাকি ছিল অপরাজেয়। বেলজিয়ামে তাঁদের সঙ্গে একই বাসায় থাকতেন বাংলাদেশের আবদুল মজিদ মোল্লা। তিনি ও তাঁর স্ত্রী আয়েশা দুজনই ছিলেন ডাক্তার। তাঁদের মধ্যে ছিল বন্ধুত্ব, কিন্তু ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে তাঁদের প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ডা. আবদুল মজিদ মোল্লা আর তাঁর স্ত্রী উৎফুল্ল ছিলেন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে। ড. আবদুল কাদির খানের মনে ছিল দেশ ভাঙার বেদনা। কিন্তু এতে তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বে ভাটা পড়েনি কোনো দিন। ড. মোল্লা আর তাঁর স্ত্রী এখন আছেন সৌদি আরবে, বললেন ড. খান।
১৯৭১ সালের বিয়োগান্তক ঘটনার পর ১৯৭৪ সালে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ ড. খানের ধারণায় ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর উপলব্ধিতে স্বাধীন দেশ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য পাকিস্তানের দ্রুত পারমাণবিকায়ন ছাড়া তখন কোনো বিকল্পই ছিল না।
জুলফিকার আলী ভুট্টো তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে ড. খান ভুট্টোকে চিঠি লিখলেন। বৈজ্ঞানিক হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে তিনি তাঁকে জানালেন যে পাকিস্তানে পারমাণবিক প্রকল্পে তাঁর সাধ্যমতো অবদান রাখতে তিনি আগ্রহী। দশ দিনের মধ্যেই ভুট্টো তাঁর চিঠির উত্তর দিলেন, আমন্ত্রণ জানালেন তাঁকে পাকিস্তানে। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরেই তিনি দেখা করলেন ভুট্টোর সঙ্গে পাকিস্তানে। তারপরই হল্যান্ডে পাকিস্তানের দূতাবাস মারফত ভুট্টো ড. আবদুল কাদির খানের যোগ্যতা যাচাই করলেন। ১৯৭৫ সালের ডিসেম্বরে সস্ত্রীক তিনি যখন পাকিস্তানে, ভুট্টোর সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হলো। তাৎক্ষণিকভাবে ভুট্টো তাঁকে পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রকল্পের দায়িত্বভার নেওয়ার অনুরোধ করলেন। হল্যান্ডে ফিরে না যাওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ জানালেন। সেদিনই ইসলামাবাদে তাঁর স্ত্রী হেনির কাছে তিনি ব্যক্ত করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবটি। তাঁর স্ত্রীর জন্য এই প্রস্তাব গ্রহণের অর্থ ছিল এই যে তাঁকে চিরদিনের জন্য নিজ দেশ ছেড়ে পাকিস্তানেই বসবাস করতে হবে। একটিমাত্র প্রশ্নই হেনি করলেন তাঁর স্বামীকে। তা হলো, ‘তুমি কি সত্যি মনে করো, তুমি তোমার দেশের জন্য কিছু করতে পারবে?’ মাথা নাড়লেন ড. খান। ‘তাহলে তুমি থেকে যাও। আমি হল্যান্ডে ফিরে গিয়ে সংসার গুটিয়ে ফিরে আসি।’ তা-ই হলো। দেশেই থেকে গেলেন ড. আবদুল কাদির খান।
তারপরের ইতিহাস সংকল্প, সাধনা আর সাফল্যের ইতিহাস। অনিশ্চিত রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্যেও তিনি সহায়তা ও সহযোগিতা পেয়েছেন সেই দেশের পরবর্তী প্রতিটি সরকার আর সরকারপ্রধানের-ভুট্টো, জিয়াউল হক, গোলাম ইসহাক খান আর দুবার করে বেনজির ভুট্টো ও নওয়াজ শরিফের। পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধানকে পাকিস্তানের পারমাণবিক প্রকল্প সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা হয়নি, জানালেন ড. খান।
দেশে কাজ করতে গিয়ে আবদুল কাদির খানের প্রথম উপলব্ধিই ছিল এই যে পাকিস্তান পারমাণবিক কমিশনে থেকে সাফল্য অর্জন অসম্ভব। সেটি আমলাদের কলম পেষার একটি অফিস। তাঁকে কমিশনের চেয়ারম্যান করার প্রস্তাবটিও প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। ড. খান প্রস্তাব করলেন যে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অন্য একটি সংস্থা সৃষ্টিতে তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হোক। এক দিনের মধ্যেই ভুট্টো রাজি হলেন সেই প্রস্তাবে। স্থাপিত হলো কাহুটার ইস্টার্ন রিসার্চ ল্যাবরেটরি। পরে জেনারেল জিয়ার আমলে যার নামকরণ হলো ড. আবদুল কাদির খানেরই নামে। তবে প্রথম ছয় মাস মাইনে পাননি তিনি। তারপর মাসে তিন হাজার টাকা। আর কিছুদিন পর তাঁর জন্য মঞ্জুর হলো শতকরা ২৫ ভাগ বিশেষ ভাতা।
১৯৭৬ সালের এপ্রিল থেকেই কাহুটায় কর্মকাণ্ডের শুরু। কাহুটা স্থানটি নির্বাচন নিজেই করেছিলেন ড. খান। রাজধানী আর বিমানবন্দরের কাছাকাছি নিরিবিলি কাহুটা, যেখানে গোপনীয়তা রক্ষা করা ছিল সম্ভব। গবেষণার জন্য প্রয়োজন ছিল বিশাল নির্মাণকাজের, যার ভার তিনি আর্মি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। কন্ট্রাক্টর আর টেন্ডারের ঝামেলা তাঁকে পোহাতে হয়নি, জানালেন ড. খান। গবেষণার জন্য তাঁকে নিয়োজিত করতে হয়েছিল শত শত বৈজ্ঞানিককে। তাঁদের প্রশিক্ষণ এবং প্রেষণ ছিল একটি অতিপ্রয়োজনীয় দায়িত্ব। ইউরোপে আহরিত জ্ঞান তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন কাহুটায়। যখন কোনো যন্ত্র অথবা যন্ত্রাংশ কেনার প্রয়োজন হয়েছে, বিদেশ থেকে তিনি তা ক্রয় করতে সক্ষম হয়েছেন, আর যেখানে সম্ভব, আত্মনির্ভরশীল হয়ে তাঁরা নিজেরাই প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ নির্মাণ করেছেন। কাহুটার সাফল্য সবার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায়, বললেন ড. খান।
ড. খানের ভাষায়, কাহুটার গবেষণাগারটি পাকিস্তানকে দিয়েছে বিশ্বের পারমাণবিক মানচিত্রে একটি স্থায়ী আসন। সেখানে তৈরি ৩% থেকে ৩.৫% সমৃদ্ধকৃত ইউরেনিয়াম জ্বালানি হিসেবে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সব পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরে ব্যবহৃত হতে পারে। তাঁর মতে, ১৯৭৪ সালে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ উপমহাদেশের সামরিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। এর ফলেই ১৯৭৬ সালে পাকিস্তানকে স্থাপন করতে হলো ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ল্যাবরেটরি, যেখানে মাত্র ছয় বছরের মধ্যেই পাকিস্তান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের ক্ষমতা অর্জন করল। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি আমাকে জানালেন, ভারতের পোখরানের পারমাণবিক বিস্ফোরণ না হলে পাকিস্তান কখনোই চাঘাইতে বিস্ফোরণ ঘটাত না। ড. আবদুল কাদির খান মনে করেন, দেশে জনপ্রিয়তা লাভের জন্যই বিজেপি সরকার এ পদক্ষেপ নিয়েছিল। এখন উপমহাদেশে যে পারমাণবিক প্রতিযোগিতা শুরু হলো, এতে হবে অর্থের বিপুল অপচয়, মন্তব্য করলাম আমি।
ড. খানের মতে, ‘পাকিস্তানের আর পারমাণবিক প্রতিযোগিতার কোনো প্রয়োজন নেই। ভারতের যেকোনো স্থানে পারমাণবিক আঘাত হানার সামর্থ্য অর্জনই পাকিস্তানের জন্য যথেষ্ট। আমরা ভারতের ওপর ধ্বংসাত্মক হামলা চালাতে পারি, তারাও পারে আমাদের ওপর। এরপর অন্তত আর পাকিস্তানের প্রতিযোগিতার প্রয়োজন নেই। ভারতের যদি অন্য কোনো লক্ষ্য থেকে থাকে, সে সমস্যা তাদের। আমাদের লক্ষ্য শুধু ভারত।’
এই শিহরণ জাগানো কথাগুলো ড. আবদুল কাদির খান উচ্চারণ করলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নম্রতায়। আবার ব্যক্ত করলেন এই আশাবাদ যে পারমাণবিক ভারসাম্যের কারণে পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে পারমাণবিক সংঘাত হওয়ার আশঙ্কা নেই।
আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন যে কাহুটায় পারমাণবিক গবেষণায় যা খরচ হয়েছে, তা একটি এফ-১৬ জঙ্গি বিমানের মূল্যের চেয়েও কম। পারমাণবিক গবেষণায় অর্থ নয়, জ্ঞান আর বুদ্ধির প্রয়োজন, বললেন ড. খান। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মকে কি তাঁর কিছু বলার আছে, তাঁকে আমার শেষ জিজ্ঞাসা। হ্যাঁ, বললেন তিনি। বললেন, তাদের উচিত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ওপর জোর দেওয়া। দেশের অগ্রগতি মূলত তার ওপরই নির্ভরশীল। তিনি আরও বললেন, বাংলাদেশ সরকারের কাছে তাঁর অনুরোধ, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির জ্ঞানচর্চায় অর্থের যেন কোনো কার্পণ্য না হয়।
এই ‘ধর্মের কাহিনি’ আমাদের এই দেশে কাকে শোনাই? আমার নিজের কাছেই আমার এই জিজ্ঞাসা!
(লেখাটি ফারুক চৌধুরীর ‘অনাবিল মুখচ্ছবি’ বই থেকে নেওয়া)