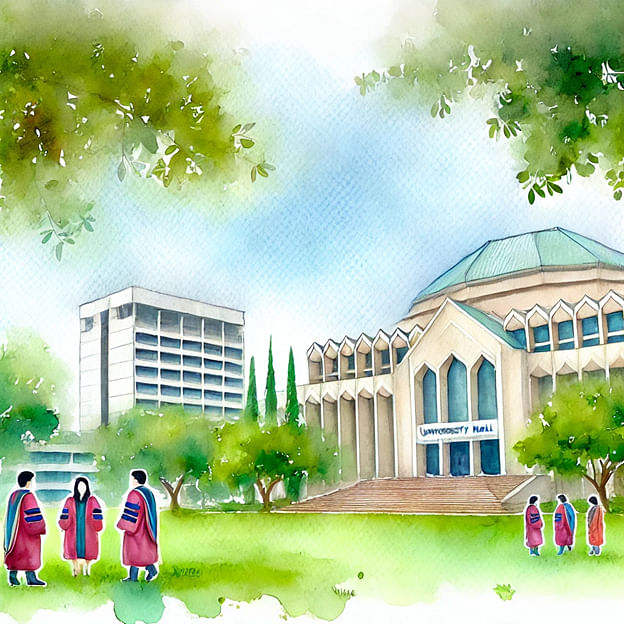আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি পাঁচ বছর। সেশনজটে আটকে পাস করে বের হতে হতে লেগে গেল প্রায় বছর সাতেক। এই সাত বছর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমার স্বপ্নভঙ্গের বছর। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠতে না পারার বেদনা প্রত্যক্ষ করেছি কাছ থেকে।
আরও পরে বুঝেছি, আমাদের দেশে কেন আসলে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। এই না থাকার হাহাকার নিয়ে বিদগ্ধজনেরা অনেকেই লিখেছেন, লিখছেন। আমি খুব আশা করে আছি, আমাদের তরুণ প্রজন্ম বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তাদের ক্ষোভ, হতাশার কথা নিয়মিত লিখবে। লিখবে কেমন বিশ্ববিদ্যালয় তারা চায়, যেখানে দলীয় লেজুড়বৃত্তির ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি থাকবে না, থাকবে না গণরুম, হল দখল আর বাজে খাবারের ক্যানটিন। আমি তরুণদের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তারুণ্যের ইশতেহার চাই নিয়মিত।
জানি, পাল্টাতে হবে অনেক কিছুই। তবে আজকের এই লেখায় আমি শুধু ‘গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ের’ শুরুটা কেমন করে হতে পারে, তা নিয়ে বলব। এই সময়ে দাঁড়িয়েও আমাকে এই শব্দযুগল ব্যবহার করতে হচ্ছে খুব হতাশা নিয়েই। গবেষণা ছাড়া আবার বিশ্ববিদ্যালয় হয় কেমন করে! জ্ঞান উৎপাদনের কারখানা না হয়ে কি বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া যায়? কিন্তু আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখেছি, সেটা হয়েছে আমাদের দেশে, জেলায় জেলায়; সেগুলোকে ভালোবেসে আমরা নাম দিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয়! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞান বিতরণের কিছু দায়সারা কাজের মধ্যেই এগুলো সীমাবদ্ধ।
জ্ঞানসৃষ্টির আনন্দযজ্ঞে কীভাবে আমাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পরিণত করা সম্ভব?
উত্তরে অনেকেই দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের কথা বলেন। অনেক বিনিয়োগ প্রয়োজন, গবেষণা ফান্ডের অপ্রতুলতা দূর করতে হবে, অবকাঠামো ঢেলে সাজাতে হবে, শিক্ষকদের গবেষণার সক্ষমতা বাড়াতে হবে, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে, আরও কত কী। এই সবই সত্যি। কিন্তু আগেই বলেছি, এ লেখার বিষয় শুধু শুরু নিয়ে—গবেষণার সংস্কৃতি তৈরিতে কীভাবে আমরা একটা ভালো শুরু করতে পারি, ইংরেজিতে যাকে বলে কিকস্টার্ট। রাতারাতি সব বদলে দেওয়া সম্ভব নয়, কিন্তু আমি মনে করি, প্রাথমিক কিছু সাহসী সিদ্ধান্ত আজকেই নেওয়া যায়, যা হতে পারে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভবিষ্যৎ পাল্টে দেওয়ার প্রথম ধাপ। এই ছোট কিন্তু শক্তিশালী নীতিগত পরিবর্তনগুলোই হয়ে উঠতে পারে বড় পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি। এমন তিনটি পরিবর্তন নিয়ে আজ আসুন কথা বলি।
১. নিয়োগে পরিবর্তন
সত্যিকারের বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে হলে প্রথমেই দরকার নিয়োগপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা। বর্তমানে সিজিপিএ বা পরীক্ষার ফলাফলই নিয়োগের প্রধান মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ও ফলাফল নিয়ে উন্মাদনাই মূলত এর জন্য দায়ী। এ থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং মাধ্যমিক থেকে সর্বস্তরে পরীক্ষাকে ডি–সেনসিটাইজ করতে হবে। নিয়োগপ্রক্রিয়ায় যে হাস্যকর বিধানগুলো আমি দেখি, যেমন ‘অত সিজিপিএ থাকা আবশ্যক’, ‘প্রার্থীকে বাংলাদেশি নাগরিক হতে হবে’, ‘বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ বছর’—এগুলো বাতিল করতে হবে। দুনিয়ার কোথাও এসব দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় না। প্রার্থীর গবেষণাদক্ষতা এবং তাঁর প্রকাশিত কাজগুলোর সংখ্যা ও মানই হয় নিয়োগের প্রধান মানদণ্ড।
আমরা এসবের ধার ধারি না! আমরা গবেষণা নিয়ে কোনোরকম পদ্ধতিগত প্রশিক্ষণ নেই, এমন ব্যক্তিকে শুধু যে নিয়োগই দিই, তা–ই নয়; তাঁকে নীতিনির্ধারকের ভূমিকায়ও বসিয়ে দিই। আমি আতঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করেছি, পিএইচডি নেই, এমন লোক আমার ফ্যাকাল্টির ডিন, কখনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, এমনকি ইউজিসির চেয়ারম্যানও। এমন নিয়োগের অবশ্যম্ভাবী ফল, গবেষণায় অদক্ষ ও উদাসীন একদল শিক্ষক। তাঁরা এতই অযোগ্য যে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগিতা করে কোনো স্কলারশিপ বা ফেলোশিপ পেতেও অক্ষম। শেষমেশ প্রধানমন্ত্রীর অফিসে ধরনা দিয়ে বসে থাকেন, দেশের টাকায় উচ্চতর শিক্ষার আশায়। আমরা তাই চালু হতে দেখি শিক্ষকদের জন্য বঙ্গবন্ধু ওভারসিজ স্কলারশিপ (এখানে বলে রাখি, দেশের টাকা অপচয় করে আমলাদের ডক্টর হওয়ার এমন একটি উন্নাসিক প্রকল্প ‘প্রাইম মিনিস্টার ফেলোশিপ’ কিছুদিন আগে বাতিল করা হয়েছে)।
অথচ গবেষণায় প্রশিক্ষিত, জ্ঞানসৃষ্টিতে দক্ষ একদল গবেষক আমাদের তৈরি হয়েই আছেন, যাঁরা দেশে ফিরতে উন্মুখ। মনে আছে, সেই রিভার্স ব্রেন ড্রেন হ্যাশট্যাগ? আমরা আর কতকাল তাঁদের উপেক্ষা করব? আমরা কি পারি না চীনের মতো ‘থাউজেন্ড ট্যালেন্ট প্ল্যান’ ধরনের প্রজেক্ট নিতে, কিংবা নিদেনপক্ষে ভারতের মতো নিয়ম, যেখানে বিশ্ব-র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করে এসেই সরাসরি নিয়োগ পাওয়া সম্ভব? গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো এই প্রতিভাবানদের আকর্ষণ এবং তাঁদের ধরে রাখা। এর জন্যে আমাদের প্রতিযোগিতামূলক বেতন কাঠামোও দরকার, যা শিক্ষকদের যোগ্যতা ও গবেষণার যথাযথ মূল্যায়ন করবে। আমাদের সেটি পর্যায়ক্রমে অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু শুরুর কাজটি কি আমরা এখনই করতে পারি না? নিয়োগপ্রক্রিয়ার ঘুণে ধরা বিধানগুলো বাতিল করে গবেষণার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাই হোক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার প্রধান মাপকাঠি।
২. পদোন্নতিতে পরিবর্তন
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পদোন্নতি হয় মূলত বছর গুনে। খুবই আশ্চর্য ব্যাপার, কিন্তু দেশে এটাই নিয়ম। ক্ষেত্রবিশেষে উচ্চতর ডিগ্রি থাকলে বছরসংখ্যায় ছাড় দেওয়া হয়। আর নিয়োগ, পদোন্নতি—সবকিছুতেই রাজনৈতিক বিবেচনা তো আছেই; সেই আলোচনায় আজ না–ই গেলাম। বছরের হিসাবের পাশাপাশি শিক্ষকদের নামকাওয়াস্তে কিছু গবেষণাও করতে হয়। বলা বাহুল্য, বেশির ভাগ সময়ই সেগুলো পদোন্নতির শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যেই করা, জ্ঞানসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা কিংবা নতুন আবিষ্কারের উৎসাহ ও আনন্দ থেকে নয়। গবেষণাগুলো যথারীতি প্রকাশিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়েরই নামসর্বস্ব কিছু জার্নালে। বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে দেখেছি, ফ্যাকাল্টির, কখনো কখনো ডিপার্টমেন্টেরও নিজস্ব জার্নাল আছে। নতুন জ্ঞান সেখান থেকে আহরণ করেছি, কিংবা সেগুলো ক্লাসে পড়ানো হয়েছে, এমন মনে করতে পারি না। শিক্ষকেরা নির্ভর করে থাকেন পশ্চিমা বইয়ের নীলক্ষেত এডিশনের ওপর অথবা ছাত্রজীবনে তাঁর নিজের করা হলদে হয়ে যাওয়া নোটবুকে।
বছর গোনার সংস্কৃতি আর গবেষণার নামে এই ট্র্যাশ উৎপাদন আমাদের বন্ধ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে এসব অগণিত মানহীন জার্নালেরও আমাদের কোনো দরকার নেই। বিশ্বের মতোই এখানেও শিক্ষকদের পদোন্নতি হোক মানসম্পন্ন গবেষণা দেখে, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ভালো জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ বিচার করে, গবেষণার সাফল্য আর প্রভাব (ইমপ্যাক্ট) বিবেচনায় নিয়ে। শিক্ষার্থী মূল্যায়নের পাশাপাশি আমরা পদোন্নতির শর্তাবলিতে যুক্ত করতে পারি ইনডেক্সড বা র্যাংকড জার্নালে প্রকাশনার সংখ্যা, যা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিশ্ব-র্যাঙ্কিংয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করতেও সহায়ক হবে।
বিশ্বমানের গবেষণা করতে হলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অত্যাধুনিক গবেষণাগার ও লাইব্রেরির প্রয়োজন, প্রয়োজন আন্তর্জাতিক জার্নালে সাবস্ক্রিপশন। আমাদের সামনেই বিশাল বিনিয়োগের উদাহরণ আছে সিঙ্গাপুর আর দক্ষিণ কোরিয়ার। উদাহরণ আছে চীনের ‘ডাবল ফার্স্ট ক্লাস’ উদ্যোগের। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অবকাঠামো আমাদের তাই ধীরে ধীরে উন্নত করতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ। কিন্তু এই যাত্রার প্রথম নীতিগত পরিবর্তনটা কি আমরা আজই করতে পারি না? ভালো গবেষণাই হোক পদোন্নতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। গ্র্যান্ট, গবেষণা ফান্ড আনতে পারার দক্ষতা, আর জ্ঞানরাজ্যে পরিচিতি—এসবেই হোক মূল্যায়ন। এতে করে শিক্ষকেরা গবেষণায় আরও আগ্রহী হবেন, তাঁদের কাজের মান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষাও উন্নত হবে।
৩. পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন
গবেষণা ছাড়া যেমন শিক্ষকদের নিয়োগ বা পদোন্নতি হবে না, তেমনি গবেষণা ছাড়া শিক্ষার্থীদেরও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন হবে না। অনেকেই অবাক হবেন, সবারই কি গবেষণা শিখতে হবে? সবাই তো আর গবেষক বা শিক্ষক হবেন না। কিন্তু আপনি সরকারি চাকরজীবী হোন কিংবা করপোরেট সিইও অথবা উদ্যাক্তা—তিনটি স্কিল আপনার লাগবেই; ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং স্কিল, প্রবলেম সলভিং স্কিল আর কমুনিকেশন স্কিল। আপনি কিছু হোন আর না হোন, জীবনে চলার পথে এই দক্ষতাগুলোর বিকল্প নেই। আর এই তিনটিই শেখা যায় গবেষণার মাধ্যমে। পাঠ্যক্রমে তাই বাধ্যতামূলকভাবে থাকুক গবেষণাপদ্ধতির শিক্ষা। গবেষণা প্রজেক্ট বা থিসিস সম্পন্ন না করে কোনো ডিগ্রি নয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের স্মৃতি থেকে বলি, শিক্ষকদের বেশির ভাগকেই দেখেছি বই থেকে আনক্রিটিক্যালি পড়ান, যেন নাজিল হওয়া কোনো কিতাব পড়াচ্ছেন। প্রশ্ন করার মানসিকতা নেই, চিন্তা করার সাধনা নেই। শুধু মেনে নেওয়া। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তো মেনে নেওয়ার জায়গা নয়; বিশ্ববিদ্যালয় হলো তর্ক করার জায়গা, প্রশ্ন করার জায়গা। আমাদের শিক্ষকদের এসব বালাই নেই। ওনারা বিনা প্রশ্নে নত মাথায় আসমানি বিদ্যা বিলি করেন শিক্ষার্থীদের। প্রশ্নহীন, নতমস্তক শিক্ষকের চেয়ে লজ্জার কোনো বস্তু আমি বিশ্ববিদ্যালয়জীবনে দেখিনি। এই অসুখের দাওয়াই হতে পারে গবেষণা, যার মাধ্যমে আমরা অনুসন্ধিৎসু মন তৈরি করতে পারি।
শিক্ষকদের বিনীত অনুরোধ করব, সীমিত সুযোগের দোহাই না দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়েই গবেষণার কাজে নেমে পড়ুন। আপনার আশপাশেই সফল উদাহরণ পাবেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন বেশ কজন শিক্ষককে জানি, যাঁরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে দেশে বসেই বিশ্বমানের গবেষণা করে যাচ্ছেন। আশা করব, এসব উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হয়েই থাকবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি, এমন শিক্ষক আছেন, যিনি ভালো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করে ফিরে এসে হাত-পা ছেড়ে বসে আছেন। গবেষণাবিমুখ, রাজনীতিমুখর। ছাত্রজীবনে আমার কিছু গ্লানির মধ্যে একটি হলো আমি দেখেছি শিক্ষকেরা কীভাবে শিক্ষার্থীদের প্রায় পাড়ার মাস্তানের মতো বকা দেন, ভর্ৎসনা করেন; দেখেছি তাঁদের আস্ফালন, নিপীড়ন। আমি আশা করি, নিয়োগ বা পদোন্নতিতে পরিবর্তনের পাশাপাশি পাঠে গবেষণার অন্তর্ভুক্তিকরণ এ অবস্থার উত্তরণ ঘটাবে।
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে সিনিয়র-জুনিয়র স্কলারের সম্পর্ক। শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের সহযোগী স্কলার হিসেবে ভাববেন, সম্মান দেবেন। একই সঙ্গে তাঁদের এই গবেষণাযজ্ঞের যাত্রা শুরু হতে পারে পাঠ্যক্রমে কিছু নীতিগত পরিবর্তন করেই।
পরিশেষে বলি, আমাদের লক্ষ্য একটাই—বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা। আমি এমন কোনো দেশের নাম মনে করতে পারি না, যারা বড় বিশ্ববিদ্যালয় না গড়ে দেশ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে। একটা দেশ বড় হওয়ার পূর্বশর্ত তার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বড় হওয়া। বিশ্বমানের না হয়ে, বিশ্বের জন্য না হয়ে, পাড়ায়-গঞ্জে শুধু নামে বিশ্ববিদ্যালয় বানিয়ে ছেয়ে ফেলার কোনো মানে নেই। চলুন, স্বপ্ন দেখি এমন এক বাংলাদেশের, যেখানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। যেখানে গবেষণায় সৃষ্টি হয় নতুন জ্ঞান, উদ্ভাবিত হয় নতুন প্রযুক্তি, যা শুধু দেশ নয়, পুরো বিশ্বের জন্যও উপকারী। সেটাই হবে আমাদের গৌরবের দিন, আমাদের মাথা তুলে দাঁড়ানোর দিন।
এই স্বপ্নকে বাস্তব করতে হলে এখনই আমাদের পরিবর্তনযাত্রার সূচনা করা জরুরি। ছোট কিছু নীতিগত পদক্ষেপ দেশের উচ্চশিক্ষা–ব্যবস্থাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে, যেখানে গবেষণাই হবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রাণশক্তি। আমাদের শুরু করার উৎকৃষ্ট সময় এখনই। জুলিয়াস সিজার থেকে মনে পড়ছে,
‘On such a full sea are we now afloat,
And we must take the current when it serves,
Or lose our ventures.’
আমি যাত্রার শুরুটা দেখব বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। আমাদের হেরে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই।
লেখক: মোহাম্মদ জইনুদ্দিন, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ক্যানবেরা, অস্ট্রেলিয়া
দূর পরবাসে ছবি ও লেখা পাঠাতে পারবেন পাঠকেরা। ই-মেইল: dp@prothomalo.com