তখনকার ঈদ, এখনকার ঈদ
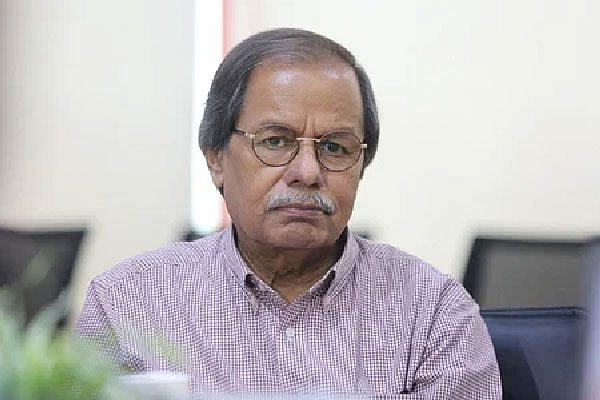
পেছন ফিরে তাকালে আমার অবাক লাগে, ঈদুল আজহা, যাকে আমরা বলতাম কোরবানির ঈদ, একুশ শতকের এই সময়ের চেয়ে কতটা যে অনাড়ম্বর ছিল! কিন্তু উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস আর আনন্দের তো কোনো ঘাটতি ছিল না।
ছেলেবেলার সময়টা স্কুলের, খেলার মাঠের, বন্ধুসঙ্গের, নিরুদ্বেগ সময়ের। ৬০ বছর আগে এই সময়টা আমি কাটিয়েছি, যখন আমার মফস্সল শহরে কারও বাড়িতে বিদ্যুৎ থাকাটা ছিল ব্যতিক্রম, মিডিয়া বলতে ছিল রেডিও এবং খবরের কাগজ (যা আমার সিলেট শহরে পৌঁছাত বিকেল-সন্ধ্যায়); এবং দৃশ্যমাধ্যম বলতে ছিল সিনেমা, যা দেখার অনুমতি পাওয়া যেত কালেভদ্রে। কাজেই সিনেমা দেখাটা ছিল উদ্যাপনের একটা বিষয়, যদিও উদ্যাপনের উপলক্ষগুলো ছিল সীমিত, আয়োজন ছিল বাহুল্যবর্জিত। জন্মদিন উদ্যাপিত হতো পরিবারের ভেতরে, জন্মদিনের কেক কী জিনিস, অনেকেই তা জানতেন না। নববর্ষ অথবা নবান্ন—এ রকম উৎসব তখন উৎসব ছিল না, ছিল নিতান্তই আটপৌরে, অন্তরঙ্গ কৃত্য, যদিও আনন্দের তাতে কমতি ছিল না। বড় মাপের উদ্যাপন হতো ঈদে ও পূজায় এবং সেগুলোতে আমন্ত্রণ থাকত সবার।
দিনরাত জেগে থাকা টিভি ছিল না বলে ঈদে বাড়ি যাওয়া নিয়ে কারও মাথাব্যথা ছিল না, ট্রেন-বাসের অগ্রিম টিকিট কাটার বিড়ম্বনাও ছিল না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছিল না, তাই ঈদ উৎসব হারিয়ে যেত না নানান লোকদেখানো ভিডিও এবং ‘কনটেন্ট’-এ, যার প্রকাশ কেনা-গরু থেকে নিয়ে ঈদের পোশাক, ঈদের ছুটিতে কক্সবাজারের সৈকতে লাখো মানুষকে পেছনে রেখে তোলা সেলফি থেকে নিয়ে রান্নার ছবির মিছিলে।
কিন্তু দেখানোর চেয়ে সময়টা বরং ছিল দেখার—যে অর্থে দেখা হচ্ছে, চোখ মেলে ভুবন দেখা থেকে নিয়ে মানুষের যত্নে দৃষ্টি দেওয়া। বয়স্করা দেখতেন যেন কোনো গরিব মানুষ কয়েক টুকরা মাংস না নিয়ে ফিরে যায় বা বিপন্ন প্রতিবেশী ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়। এ ছিল দৃশ্যমানতার বিপরীতে অদৃশ্যমানতার ‘কনটেন্ট’-মেন্ট বা তৃপ্তি।
আমাদের ছেলেবেলায় অনলাইন গরুর হাট ছিল না। উদ্যোক্তাদের বিরাট ছবিসহ বিরাট গরুর হাটের বিজ্ঞাপনও শহরজুড়ে ঝুলত না। কিন্তু গরুর হাট কোথাও না কোথাও বসত, মানুষ গরু-ছাগলও কিনত, কিন্তু সবার হাতে পয়সা ছিল না বলে শেয়ারেই বেশির ভাগ কোরবানি হতো। কোনো বাড়িতেই ফ্রিজ ছিল না, ডিপ ফ্রিজে সারা বছরের মাংসের জোগান রাখার কথাই ওঠে না। কোরবানি ছিল যতটা না নিজের জন্য, তার চেয়ে বেশি মানুষের জন্য।
আমাদের ছেলেবেলার ঈদের কেনাকাটাও ছিল ঘরোয়া। তাতে মা-আপাদের অংশগ্রহণ ছিল না। যা কেনার তা বাবা-চাচারাই কিনতেন। শপিং মল ছিল না, কেনাকাটার ঘনঘটাও তাই ছিল না। চাহিদা যেটুকু ছিল, তার অল্পখানিক জোগান হলেই পরিবারগুলো সন্তুষ্ট থাকত।
আমাদের পরিবারটিতে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল, যেহেতু মা–বাবা দুজনই চাকরি করতেন। কিন্তু ভোগের পেছনে খরচটাকে অনৈতিক বলেই ধরে নেওয়া হতো। এই বোধটা কমবেশি সব পরিবারের ভেতরেই ছিল। সে জন্য প্রতি ঈদে নতুন জামা-জুতা পাওয়াটা কারও ভাগ্যে জুটত না। এক ঈদে আমার এক বন্ধু, যার বাবা ছিলেন লন্ডনি, এক নতুন বাহারি শার্ট পরে মাঠে এল (ঈদের দিনের একটা সময় আমরা মাঠেই কাটাতাম)। শার্টটা তার বাবা ছুটিতে নিয়ে এসেছিলেন। সেই শার্ট পরে বন্ধুটি যখন ময়ূরের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে তার বাবা তা দেখে ছেলেকে ডেকে নিয়ে গেলেন। একটু পরেই বন্ধুটি ফিরল, তার পরনে পুরোনো একটা শার্ট। তার বাবা দেখেছেন, অন্য অনেকের গায়ে নতুন শার্ট নেই, নতুন বাহারি শার্ট তো দূরের কথা। ছেলেকে তিনি কারও মনের কষ্টের কারণ হতে দেননি।
এক ঈদে আমাদের পাড়ায় হঠাৎ শোরগোল উঠল, ‘গরু ভাগি গেছে।’ আমাদের বাসা থেকে একটু দূরে এক পশু-ডাক্তার, অর্থাৎ ভেটেরিনারিয়ান থাকতেন। রাস্তার পাশে পশু চিকিৎসালয়, পেছনে তাঁর বাসা। আগের দিন তিনি একটা গরু কিনেছেন। কয়েকজন মিলে কোরবানি দেবেন, সকালে সেই গরুর গলায় লাগানো দড়িটা একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে, তার সামনে ঘাসপাতার একটা স্তূপ রেখে সেই পশু চিকিৎসক নামাজে গেছেন। ফিরে এসে দেখেন, দড়ি ছিঁড়ে গরু হাওয়া হয়ে গেছে। গরু খোঁজা শুরু হলো। গরুটা কেউ চুরি করেছে, নাকি নিজেই সে পালিয়েছে—এ নিয়ে জল্পনা–কল্পনা ডানা মেলল। কেউ একজন বলল, গরুরা রাগলে দড়ি ছিঁড়তে পারে। যেমন ছিঁড়েছে জয়নুল আবেদিনের ‘বিদ্রোহী’ গরু। না, শেষ কথাটা ওই একজনের না, আমার। খোঁজাখুঁজির একটা সময় গরুটাকে নিয়ে কেউ একজন হাজির হলো। একটা উল্লাসধ্বনি উঠল, কিন্তু পশু চিকিৎসক বললেন, ‘এই গরু সেই গরু না।’ তাঁর অংশীদারেরা বললেন না, ‘এটাই তো সেই গরু।’ চিকিৎসক বললেন, ‘না। এটা অন্যের গরু।’ একটা তর্ক উঠল। কিন্তু ডাক্তার সাহেব তাঁর বক্তব্যে অটল। ‘আমি তো এই পশুদের ডাক্তার’, তিনি বললেন, ‘আমার চাইতে গরুদের কে ভালো চেনে, বলুন?’
তাঁর কথা না মেনে উপায় নেই।
ঘণ্টাখানেক পর গরুর আসল মালিক এক গোয়ালা এসে উপস্থিত। গরুর দুধ বিক্রি করে তিনি সংসার চালান। তাঁর উঠান থেকে কেউ এসে গরুটা নিয়ে গেছে। তিনি বাইরে ছিলেন, ফিরে এসে দেখেন এই বিপত্তি।
একুশ শতকের এই সময়ে শেষ দৃশ্যটা কী হতে পারত, তা ভেবে কষ্ট হয়। আর ওই গোয়ালার জন্য আনন্দ হয়, তিনি ওই সময়ে জন্মেছিলেন বলে।
পশু চিকিৎসকের বাড়িতে সেদিন মাংসের অভাব হয়নি। দুপুরের পর আমাকেও খবরের কাগজে মোড়ানো অল্পখানি মাংস নিয়ে তাঁর বাসায় যেতে হয়েছিল।
এই বাসায়-বাসায় মাংস বিলি করাটা আমার জন্য ছিল ঈদের দিনের সব থেকে নিরানন্দ জিনিস, কিন্তু এতে সবাই আনন্দ পেত—ভাগ করার আনন্দ। পরিবারটা যদি হয় পিরামিড, বাবারা থাকতেন শীর্ষে, আর মায়েরা তাঁদের খানিক নিচে। আমার মতো সেজ ছেলেদের জায়গা হতো এর ভেতরে; এবং আমাদের ভাগ্যে থাকত মাংস বণ্টন। কিন্তু এই হায়ারার্কি তখন এমন ছিল যে এর সঙ্গে ইয়ার্কি চলত না।
একটা জায়গায় অবশ্য হায়ারার্কির ওলটপালট হতো—তা ছিল ঈদের ভোজে। ঈদের রান্না কী হবে, কতটা হবে, কী কী পদ হবে—তার সব নির্ধারণ করতেন মায়েরা, অর্থাৎ পিরামিডের শীর্ষে তখন তাঁরা।
স্বল্পমেয়াদি এই শিথিল পিরামিডের আশকারায় আমার ছেলেবেলার ঈদগুলো ছিল বিমলানন্দের।
ছেলেবেলায় কখনো শুনিনি ঈদে মসলাপাতির দাম বাড়ানো হয়েছে, দাম আকাশ ছুঁয়েছে। এখন ঈদের মাসখানেক আগে থেকেই দাম বাড়ানো নিয়ে মিডিয়া শোরগোল শুরু করে। ব্যবসায়ীরা এই শোরগোল শুনে আনন্দে-উত্তেজনায় দাম বাড়ান, নাকি দাম বাড়ান বলে মিডিয়া উত্তেজিত শোরগোল তোলে এবং একটা অনতিক্রান্ত চক্র তৈরি হয়? কে জানে।