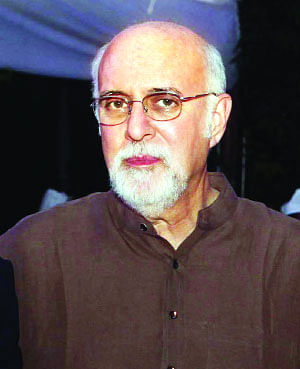
পরবর্তী কয়েক বছরে এরশাদ ও তাঁর সহযোগীরা ‘বিক্ষুব্ধ সেনা’, ‘উত্তেজিত জনতা’ এবং ‘বিক্ষুব্ধ মানুষের’ হাতে মঞ্জুর হত্যার অনেক কাহিনি ফেঁদেছেন।
২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে বার্তা সংস্থা বিডিনিউজ-২৪ এই মামলার হাজিরায় এরশাদের এই বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে, ‘চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে আনার পর উত্তেজিত জনতা মঞ্জুরকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এই টানাহ্যাঁচড়ার মধ্যে নিরাপত্তারক্ষীরা গুলি ছুড়তে বাধ্য হয়। একপর্যায়ে মঞ্জুর গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।’
এরশাদের এক সহকর্মী মোস্তফা—লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোস্তফা কামাল ২০১৩ সালে আদালতে বলেছিলেন, ‘কিছু বিক্ষুব্ধ মানুষ চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে মঞ্জুরকে নেওয়ার পথে তাঁকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এতে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে তাদের গুলিবিনিময় হয়। একপর্যায়ে মঞ্জুরের গায়ে বুলেট বিঁধে। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।’
এরশাদ ও তাঁর সহযোগীরা যে গল্প ফেঁদেছেন এবং ৩০ বছর ধরে ভাঙা রেকর্ডের মতো বাজিয়ে চলেছেন, তার প্রধান দুর্বলতা হলো বাস্তবের সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। সে সময় চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন বা এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা কেউই কখনো বলেননি যে তাঁরা ‘বিক্ষুব্ধ মানুষ’ বা ‘বিক্ষুব্ধ অস্ত্রধারী’ ব্যক্তিদের দেখেছেন, যাঁরা মঞ্জুরকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে গোলাগুলি হয়; আর মঞ্জুর এই ‘টানাহ্যাঁচড়া’র কারণে গুলিবিদ্ধ হন। কেউ কেউ বলেছেন, মঞ্জুরের ‘নিরাপত্তারক্ষীরা’ গুলি করেছিল; আর কেউ বলেছেন, ‘হাসপাতালে নেওয়ার পথে মঞ্জুর মারা যান।’ কিন্তু কোনো হাসপাতালেই মঞ্জুরকে সেদিন জীবিত বা মৃত বা আহত অবস্থায় দেখা যায়নি। কেবল একজন সেনা চিকিৎসক তাঁকে দেখেছেন। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের ব্রিগেডিয়ার আজিজ, ক্যান্টনমেন্টের দায়িত্বে তখন ছিলেন তিনি, দাফনের জন্য মরদেহ প্রস্তুত করাতে তাঁকে মঞ্জুরের ‘ক্ষত ব্যান্ডেজ’ করে দিতে বলেন।
জিয়াউদ্দীন চৌধুরী তাঁর বইয়ে ফটিকছড়িতে মঞ্জুরের শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণ এবং তাঁর গতিবিধির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর বিবরণ বা চট্টগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শীদের কারও কথার সঙ্গেই এরশাদ ও তাঁর সহযোগীদের গল্পের ন্যূনতম কোনো মিল নেই। চট্টগ্রামের তৎকালীন জেলা প্রশাসক হিসেবে জিয়াউদ্দীন চৌধুরী ১ জুন মঞ্জুরের গ্রেপ্তার হওয়া থেকে শুরু করে হাটহাজারী থানায় সেনাবাহিনীর হাতে তাঁকে সোপর্দ করা পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন। এমনকি মঞ্জুর নিরাপদে ক্যান্টনমেন্টে পৌঁছালেন কি না, সেটিও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ারের কাছ থেকে তিনি শুনে নিশ্চিত হয়েছেন।
জিয়াউদ্দীন চৌধুরীর ভাষ্যের সঙ্গে এরশাদের ভাষ্যের তুলনা করা যাক:
‘মঞ্জুর হত্যাকাণ্ডের পরদিন সরকারি তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে নেওয়ার পথে বিক্ষুব্ধ সৈন্যদের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে মঞ্জুর মৃত্যুবরণ করেছেন। এই প্রতিবেদন ছিল একটি ডাহা মিথ্যা।
‘ক্যান্টনমেন্টে নেওয়ার পথে মঞ্জুরকে হত্যা করা হয়নি। ব্রিগেডিয়ার আজিজ পুলিশের ডিআইজিকে বলেছিলেন, ২ জুন সকালবেলা মঞ্জুরকে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে হত্যা করা হয়। আজিজ এ কথা বলেননি যে মঞ্জুর বিক্ষুব্ধ সৈন্যদের হাতে মারা পড়েছেন...
‘চিকিৎসককে যখন মঞ্জুরের “ক্ষত ব্যান্ডেজ” করতে বলা হয়, তখন তিনি দেখতে পেলেন, একটিমাত্র গুলির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। গুলিটি তাঁর মাথা ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর জন্য একঝাঁক বুলেট দরকার হয়নি...ঢাকা থেকে আসা এক সেনা কর্মকর্তা মঞ্জুুরকে হত্যা করেন, বিক্ষুব্ধ সৈন্যরা নয়। তাঁকে কেন হত্যা করা হবে? কেন বিচারের মুখোমুখি করা হবে না? তিনি কি এমন কিছু জানতেন, সেনাবাহিনী যা প্রকাশিত হতে দিতে চায়নি?’
এ ধরনের মিথ্যা ও প্রচ্ছদকাহিনির সমস্যা হচ্ছে, এর প্রণেতারা অনেক সময় নিজেদের লেখা চিত্রনাট্য নিজেরাই ভুলে যান। নিজেদের গা বাঁচাতে ‘বিক্ষুব্ধ সৈন্য’দের হাতে মঞ্জুর হত্যাকাণ্ডের যেসব গল্প এরশাদ ও তাঁর সহযোগীরা ফেঁদেছেন, তার প্রতিটিতে বলা হয়েছে যে পুলিশ তাঁকে সেনাবাহিনীর বিশেষ ইউনিটের কাছে হস্তান্তর করার পর চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে ‘নেওয়ার পথে’ তাঁকে হত্যা করা হয়।
তার পরও, সিআইডির কাছে দেওয়া সাক্ষ্যে পুলিশের আইজি এ বি এম জি কিবরিয়া জানিয়েছেন, তিনি এরশাদকে সরাসরি প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে আনার পরই মঞ্জুরকে হত্যা করা হয়।’
কিবরিয়া এর আগের দিনই মঞ্জুরকে পুলিশের কাছ থেকে সেনা হেফাজতে আনার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি এরশাদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, মঞ্জুরকে কীভাবে হত্যা করা হয়?
সাক্ষ্যে কিবরিয়া বলেন, ‘২ জুন বিকেলবেলা বঙ্গভবনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আমি চিফ অব আর্মি স্টাফের কাছে জানতে চাই, মঞ্জুরকে কীভাবে হত্যা করা হয়েছে? আদতে তো তাঁর প্ররোচনায় অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি মঞ্জুরকে সেনা হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দেন, যাঁদের হাতে—এক অর্থে তাঁরই হেফাজতে—মঞ্জুরের মৃত্যু হলো। এরশাদের জবাব ছিল, চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়ার পরপরই বিক্ষুব্ধ সেনাদের গুলিবর্ষণে মঞ্জুর নিহত হন। এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দীনের মতো কিবরিয়াও এরশাদের ‘বিক্ষুব্ধ সেনা’দের হাতে মঞ্জুর হত্যার গল্প বিশ্বাস করেননি।
কিবরিয়া তাঁর সাক্ষ্যে এরশাদের নিজের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বলেছেন যে মঞ্জুরকে ‘ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়ার পথে’ হত্যা করা হয়নি। এটা একটা তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য। এরশাদের স্বীকারোক্তির পর কিবরিয়া কীভাবে ত্বরিত পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা-ও তিনি বলেছেন। প্রথমে একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাকে তিনি চট্টগ্রামে পাঠান। পরে নিজেই সেখানে যান। চট্টগ্রামে অবস্থিত তাঁর সহকর্মীদের তিনি বঙ্গভবনের বৈঠকের কথা জানিয়ে পুলিশ হেফাজতে থাকা সেনা কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা নিয়ে এই শঙ্কা প্রকাশ করেন যে সেনাবাহিনী হয়তো এদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে।
কিবরিয়া ব্যাখ্যা করেন, মঞ্জুর হত্যাকাণ্ডের পর ‘বেসামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া সেনা কর্মকর্তাদের সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য এরশাদের দাবি অগ্রাহ্য করে’ তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে তিনি কীভাবে প্রভাবিত করেন। স্পষ্টভাবেই তাঁর মনে ভয় ছিল, সেনা হেফাজতে নিয়ে গেলে এদেরও মঞ্জুরের ভাগ্য বরণ করতে হবে।
সত্যিই তাই। পরের কয়েক মাসে বহু সেনা কর্মকর্তাকে সেনা হেফাজতে এনে ব্যাপক নির্যাতন করা হয়। এরপর চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে অনুষ্ঠিত ফিল্ড কোর্ট মার্শালে তাঁদের বিচার করা হয়। ফাঁসিতে ঝোলানো হয় ১৩ জনকে। তৎকালীন অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরীর ভাষ্যমতে, এই হতভাগারা নিরপেক্ষ বিচার ও যথাযথ আইনি সুরক্ষা পাননি, যা ছিল তাঁদের মৌলিক অধিকার। আগেই বলেছি, জুলফিকার আলী মানিক তাঁর সেই সাহসী বইয়ে এসব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।
নোংরা সত্যটি হচ্ছে এই যে ওই মানুষগুলোকে এমন এক ‘অভ্যুত্থানের’ অভিযোগে বিচার করা হয়, যেটি আদতে কোনো ‘অভ্যুত্থান’ ছিল না বা সেই বিদ্রোহ কোনো দিন সম্পন্ন হয়নি। কিন্তু জিয়া আবুল মঞ্জুরের হাতে নিহত হননি; কিংবা যাঁদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে, তাঁদের হাতেও নন।
সেনাবাহিনীতে এরশাদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার অভিপ্রায়ে তাঁদের ভিত্তিহীন ও নিষ্ঠুরভাবে প্রাণ দিতে হয়। বলির পাঁঠা বানানোর জন্য এরশাদের দরকার ছিল একটি ‘অপরাধী চক্র’।
জেনারেল মইন ও জুলফিকার আলী মানিক তাঁদের বইয়ে জানিয়েছেন, এরশাদ নির্যাতন করে ‘স্বীকারোক্তি আদায় করেছেন, কিন্তু তথাকথিত বিচারটি চলেছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে, কোনো তদন্ত ছাড়াই। মেজর জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরীর নির্দেশে বিচার ও শাস্তির প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়।
খালেদা জিয়া কি সত্যি সত্যিই এরশাদকে তাঁর স্বামী হত্যার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন? প্রকৃত ‘অভ্যুত্থান’ তাহলে ঢাকাতেই হয়েছে, চট্টগ্রামে নয়।
লেখাটি ছাপাখানায় যাওয়ার পর প্রথম আলোর হাতে থাকা কিছু দলিল আমার হাতে এসেছে। দলিলগুলো হচ্ছে ১৯৮১ সালের মে-জুন মাসের সেই নিয়তি-নির্ধারক দিনগুলোতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যেসব সদস্য চট্টগ্রামে ছিলেন, সিআইডির কাছে দেওয়া তাঁদের সাক্ষ্য। এসব সাক্ষ্য আমাদের সামনে কিছু নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। এই লেখা শেষ হওয়ার পর একটি উপসংহার পর্বে সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব।
হত্যা মামলা
এসব সাক্ষ্য-প্রমাণ কী অগ্রাহ্য করা হবে? বিচারপতি কি আমার সোর্সের চূড়ান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে, নতুন এই প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য না নিয়ে তাঁর রায় ঘোষণা করবেন? যে মানুষটি বললেন, তিনি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে উপস্থিত ছিলেন, একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাকে মঞ্জুরের সেলে ঢুকতে দেখেছেন, আর সেখানেই নাকি মঞ্জুর খুন হন—তাঁর সাক্ষ্য কি উপেক্ষা করা হবে?
বিচারপতি ফিরোজ বা কোনো উচ্চ আদালত কি এই সাক্ষীর নিরাপদে সাক্ষ্য দেওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন? এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দীন, আইজিপি কিবরিয়া এবং অন্যদের দশক দশক ধরে চাপা পড়ে থাকা সাক্ষ্য কি শোনা হবে, নাকি অগ্রাহ্য করা হবে?
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কি তাঁর সদ্য নিযুক্ত ‘বিশেষ দূত’ জেনারেল এরশাদ, যিনি এ মামলার অন্যতম সন্দেহভাজন, তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক সমীকরণের স্বার্থে আপসরফা চালিয়ে যাবেন? নাকি প্রজ্ঞা জয়ী হবে? অথবা এই নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত হবে যে বিচার বিভাগের কাজে নির্বাহী বিভাগ আর হস্তক্ষেপ করবে না।
শেখ হাসিনা কি এই নতুন তথ্যের ভিত্তিতে একজন হত্যা মামলার সন্দেহভাজনের সঙ্গে রাজনৈতিক আপসরফা বন্ধ করবেন?
এরশাদ শুধু হত্যা মামলার প্রধান সন্দেহভাজনই নন, সেনাপ্রধান হিসেবে বহু সেনা কর্মকর্তাকে নির্যাতন করে তাঁদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার ঘটনায়ও তিনি একজন হুকুমের আসামি। এসব স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে তাঁদের ‘দণ্ডিত’ এবং পরবর্তীকালে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। এ ধরনের কাজ একদিকে বাংলাদেশের সংবিধানের খেলাপ, অন্যদিকে নির্যাতন এবং অন্যান্য অমানবিক ও অবমাননামূলক আচরণবিরোধী আন্তর্জাতিক রীতি-নীতিরও পরিপন্থী। তদুপরি, এরশাদ সেনাপ্রধান থাকাকালে বেশ কয়েকটি ফিল্ড কোর্ট মার্শালে বিবাদীর অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সবগুলো অপকর্মের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণের অবকাশ রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রীকে আমি বহু দিন ধরেই চিনি-জানি। আমার মনে হয় না, তাঁর সব ঔচিত্যবোধের মৃত্যু ঘটেছে। তিনিও হত্যাকাণ্ডের নির্মম শিকার হওয়া একজন মানুষের কন্যা। তাঁর নিহত স্বজনদের হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচার পেতে তিনি বহু দিন ধরে অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়েছেন। মঞ্জুরের সন্তানদের চেয়ে কি তিনি অধিকতর সুবিধাভোগী যে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারী একই রাজনৈতিক শক্তির হাতে মঞ্জুর নিহত হওয়ার পরও তাঁরা ন্যায়বিচার পাবেন না?
মঞ্জুরের পরিবারও সেই জবাবদিহি দেখতে চায়, যা প্রধানমন্ত্রী তাঁর পিতা, মাতা, ভাই, বোনদের হত্যাকাণ্ডের জন্য দাবি করেছিলেন। নতুন তথ্যের আলোকে আমরা এই প্রত্যাশা করি যে শেখ হাসিনা তাঁর ‘বিশেষ দূত’-এর কাছ থেকে সরে এসে মঞ্জুরের সন্তানদের পাশে এসে দাঁড়াবেন; তাদের বলবেন, ‘তোমাদের ন্যায়বিচারের দাবিতে আমি বিপক্ষে নই, বরং পাশে আছি।’
শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ দিল্লিতে ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে। তিনি তখন একটি সাদামাটা ঔপনিবেশিক কেতার বাংলোয় বসবাস করতেন। তাঁর নিরাপত্তা ছিল সুনিশ্চিত, তবে গোপন। দুর্বল হলেও তাঁকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন নারী বলেই আমার মনে হলো। তখনো তিনি তাঁর স্বজনদের মৃত্যুর শোক বয়ে চলেছেন। কে-ই বা এর ব্যতিক্রম? তাঁর চোখেমুখে শোক ও আতঙ্কের ছাপ ছিল স্পষ্ট। ঘরের ভেতর একটি শোকের আবহ সৃষ্টি হলো। প্রায় প্রতিটি কথাতেই তিনি অশ্রুসজল হয়ে উঠছেন। হূদয়বিদারক! ১৯৭৫ সালের ‘অভ্যুত্থানে’র পেছনের ঘটনা উন্মোচন করার জন্য আমি যে বইটি লিখেছিলাম, শেখ হাসিনা তার জন্য আমাকে ধন্যবাদ জানান।
আগস্টের সেই ঘটনার পর অনেকটা দিন চলে গেছে। তবু তাঁর সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতে অপরিমেয় সেই শোকের প্রতি আমি আমার সমবেদনা জানাই। তিনি আমার কথা শোনেন। আমি কথা বলার পর তিনি বেশ নীরব ছিলেন। ভাঙা গলায় ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানানোর পর তিনি প্রায় কোনো কথাই বলতে পারছিলেন না। আমরা তখন শোকাবহ স্মৃতি দূরে ঠেলে রেখে চা পান করতে করতে সামান্য কথা বলার চেষ্টা করি।
ঢাকায় ১৯৭৩-৭৪ সালে একজন তরুণ প্রতিবেদক হিসেবে তখনকার বিক্ষোভ ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে আমি বেশ সমালোচনামুখর ছিলাম। তার পরও সেই ‘অভ্যুত্থান’ এবং তাতে নিহত নিরীহ মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর যে ভূত আবারও জেগে ওঠে, তার খপ্পর থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো পথই খোলা ছিল না। পরবর্তী বছরগুলোতে শেখ হাসিনা দৃঢ় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭৫ সালের হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে তবেই থেমেছেন।
কিছুদিন আগে মঞ্জুরের বড় মেয়ে রুবানার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার দিল্লির সেই বৈঠকের কথা মনে পড়ে গেল। আবারও দেখলাম, পিতার মৃত্যু এবং এর পরবর্তী তিনটি দশক ধরে তাঁরা যে অমানুষিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গেছেন, সেসব কথা বলতে গিয়ে তাঁর গলা ভেঙে আসছে।
সেই আলাপচারিতার কথা বলার স্বাধীনতা আমার নেই। কিন্তু আমি জানি, সেই শোকের গভীরতা যদি অল্প কেউ উপলব্ধি করে থাকেন, তাহলে শেখ হাসিনাই তা করেছেন।
শেখ হাসিনা চাইলে তাঁর পিতা-মাতার কবরে যেতে পারেন। সব পিতা-মাতাহীন সন্তানই তা করে থাকেন। তাঁদের শেষ বিশ্রামস্থলে যাওয়া প্রতিটি মানুষের জন্যই এক গভীর সান্ত্বনার বিষয়। এটি আরও বিশেষ হয়ে ওঠে, যদি কেউ সহিংসতার কারণে মারা যান। জেনারেল মঞ্জুরের স্ত্রী ও সন্তানেরা জানেন না, তাঁদের স্বামী ও পিতার আদৌ কোনো কবর আছে কি না। সেখানে গিয়ে তাঁদের প্রার্থনা করার সুযোগটুকুও নেই।
মৃত্যুর মামলা ও সংশ্লিষ্ট সেই পরিবারের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষাকে কারোরই রাজনৈতিক ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। এটি বিবেচনাবোধহীন একটি ব্যাপার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবেদন করব, দয়া করে আপনার যে পরামর্শকেরা এর বিপরীত কথা ভাবেন, তাঁদের কথা শুনবেন না।