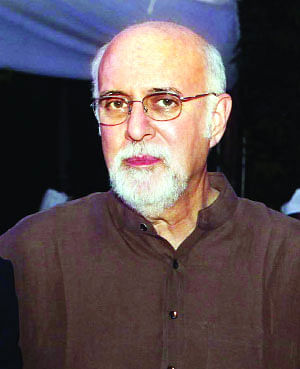
গোয়েন্দা তৎপরতায় আপনি যখন আপনার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বড় কোনো অ্যাকশনে যান এবং তা গোপন রাখার চেষ্টা করেন, তখন একটি ‘ফল্স্ ফ্ল্যাগ’ অপারেশন তৈরি করতে হয়। এই ‘ফল্স্ ফ্ল্যাগ’ এমন এক গোপন আধা সামরিক অপারেশন, যার মাধ্যমে কেউ কোনো কাজ করলে তার দায়ভার বর্তানো হয় অন্যের ওপর। এর মাধ্যমে কোনো ঘটনার সংঘটনকারীদের আড়াল করে ফেলা হয়।
লন্ডনের কিংস কলেজের গেরাইন্ট হিউজ এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেন। কোনো ‘সামরিক ও নিরাপত্তা বাহিনী পরিচালিত ঘটনার দায়ভার’ সন্ত্রাসবাদী দলের মতো অন্য কোনো সংগঠনের ওপর চাপাতে হলে কিংবা কোনো সংগঠনকে ধ্বংস করার অজুহাত সৃষ্টি করতে হলে যে ধরনের অপারেশন পরিচালনা করা হয়, এই শব্দবন্ধটি তিনি ব্যবহার করেন সেগুলোর ক্ষেত্রে। সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দাদের প্রশিক্ষণে এই ‘ফল্স্ ফ্ল্যাগ’ একটি প্রাথমিক ধারণা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ১৯৩৩ সালে রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ড বা ১৯৬৪ সালে টনকিন উপসাগরের ঘটনায় মানুষ ও গণমাধ্যমকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য এই ‘ফল্স্ ফ্ল্যাগ’ প্রমিত কৌশল হিসেবে ব্যবহার হয়।
জেনারেল এরশাদ ও তাঁর ডিজিএফআই-প্রধান মেজর জেনারেল মহাব্বত জান চৌধুরী ৩০ মে যা ঘটিয়েছেন, সেটি ফল্স্ ফ্ল্যাগের একটি ধ্রুপদি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এর সঙ্গে আবার ছিল মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অপকৌশল। জিয়া হত্যাকাণ্ডে মঞ্জুরকে জড়িয়ে ফেলা ও অবিলম্বে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ছিল তাঁদের ক্ষমতা সংহতকরণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রীয় অংশ।
মঞ্জুর জীবিত থাকলে এবং তাঁকে স্বচ্ছ বিচারপ্রক্রিয়ার মুখোমুখি করা হলে সত্য বেরিয়ে আসত। চট্টগ্রামের ঘটনা সম্পর্কে এক নতুন আখ্যান আমরা জানতে পারতাম। কিন্তু সেটি কোনোভাবেই ঘটতে দেওয়া হতো না। জেনারেল মইনের মতে যা হতো, তা হচ্ছে একটি বানোয়াট গল্প ছড়িয়ে দিয়ে জনতাকে বোঝানোর চেষ্টা করা। এরশাদের নেতৃত্বে সংগঠিত অপারেশনটি সুরক্ষা দিতে এটি জরুরি ছিল। পাশাপাশি এর নিজস্ব আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পথে বাধা দূর করা এবং সামরিক বাহিনীর সব স্তর থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিকদের অপসারণ করা।
এই প্রক্রিয়ায় পরবর্তী এক দশকের জন্য বাংলাদেশ সামরিক শাসনের খপ্পরে পড়ে। রাজনীতিতে ঘটে এক নতুন মেরুকরণ।
সেনাবাহিনীতে মুক্তিযুদ্ধের পর পাকিস্তান থেকে ফিরে আসা সেনা কর্মকর্তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য নিশ্চিত হয়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের জন্য এর এক গুরুতর আদর্শিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে।
এরশাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বহু রাজাকার, যেমন সৈয়দ মোহাম্মদ কায়সার জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন। প্রতিমন্ত্রী হিসেবে তিনি মন্ত্রিসভায়ও যোগ দেন। একাত্তরে এই কায়সার ছিলেন ‘কায়সার বাহিনী’র নেতা। বর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। হবিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলার জন্য কুখ্যাত ছিল এই কায়সার বাহিনী। পাকিস্তান বাহিনীকেও তারা সহযোগিতা করে।
এক দশকের মধ্যে সব পাল্টে গেল। পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে ঢাকা মুক্ত হয়েছিল। আর তার এক দশক পর পাকিস্তান-ফেরত সামরিক কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে দেশটিতে সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো, যারা আবার সরকারে আমন্ত্রণ জানায় রাজাকারদের। জেনারেল মঞ্জুুরের হত্যাকাণ্ডের পর যে এরশাদ ও তাঁর সহযোগীদের হাতে সুচিন্তিতভাবে সেনাবাহিনী থেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া অফিসার ও সৈনিকদের অপসারণ-প্রক্রিয়া চলে, মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সেটি আকস্মিক কোনো ব্যাপার ছিল না। আকস্মিক ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হওয়ার জন্য এই ঘটনাটি ছিল অনেক বেশি মাত্রায় আকস্মিক।
সাবেক সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হারুন-অর-রশিদ চলচ্চিত্র নির্মাতা আনোয়ার কবিরের তথ্যচিত্র ব্লাডবাথ ইন দ্য বাংলাদেশ মিলিটারির উদ্বোধনী প্রদর্শনী দেখার পর বলেছিলেন, ‘আমি মনে করি, সেনাবাহিনীতে এই অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আদলে রূপান্তর করা। এর জন্য মুক্তিযুদ্ধ-ফেরত কর্মকর্তা ও সৈনিকদের হত্যা করা জরুরি ছিল।’ জেনারেল মঞ্জুর হত্যাকাণ্ড ছিল এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
ব্যাংককে বৈঠক
জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী তাঁর বইয়ে স্বল্পজ্ঞাত এক ‘তদন্ত কোর্ট’-এর কথা উল্লেখ করেছেন। প্রেসিডেন্টের গার্ড রেজিমেন্টের অভ্যন্তরে এটা বসেছিল। গার্ড রেজিমেন্টের চারজন সদস্য ৩০ মে সার্কিট হাউসে খুন হন। ওই সদস্যদের পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার জন্য এই বিশেষ ‘তদন্ত আদালত’ গঠিত হয়। জিয়া হত্যাকাণ্ডের সময় সেখানে বেঁচে যাওয়া দুই গার্ড রেজিমেন্টের বিবৃতি এই কোর্টের প্রতিবেদনে যুক্ত করা হয়।
মইন তাঁর বইয়ে লিখেছেন, ‘দুজন সদস্যের বক্তব্য বেশ প্রণিধানযোগ্য’।
‘অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে সেই কোর্ট অব ইনকোয়ারির রিপোর্ট আমার গোচরে আসে।...তাঁদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, জিয়া হত্যার পর বিদ্রোহীরা গার্ড রেজিমেন্টের সদস্যদের সার্কিট হাউস থেকে একটি গাড়িতে করে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে নিয়ে যান। বিদ্রোহে জড়িত অফিসাররা তাঁদের গাড়িতে তোলার আগে এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন যে সেনানিবাসে যাওয়ার পর তাঁরা যেন কারও সঙ্গে কোনো কথা না বলেন। তবে যদি জিওসি জেনারেল মঞ্জুর এসে তাঁদের কাছে সার্কিট হাউসের এই রাতের ঘটনা জানতে চান তাহলে তাঁরা যেন বলেন, ‘ঝড়বৃষ্টি এবং অন্ধকারের কারণে কারা গোলাগুলি করেছে আমরা দেখিনি।’
মইন আমার কাছে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করেছিলেন। থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করার সময় তাঁর সঙ্গে মেজর খালেদ ও মেজর মোজাফফরের একটি বৈঠকের কথা তিনি আমাকে বলেন। এ দুই তরুণ অফিসার ৩০ মে ১৯৮১-এর সেই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতে জিয়াকে তুলে আনতে গিয়েছিলেন। ঢাকায় মইনের আটপৌরে ফ্ল্যাটের ছোট গ্রন্থাগারে বসে তাঁর সঙ্গে যে আলাপ হয় তার সারসংক্ষেপের বদলে বইটি থেকে উদ্ধৃত করাই সম্ভবত উত্তম হবে।
খালেদ ও মুজাফফরের সঙ্গে মইন তাঁর বৈঠকের বিবরণ এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য বইটিতে এভাবে দিয়েছেন:
‘আমি যখন থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত (১৯৮৯-৯৩) তখন জিয়া হত্যায় অভিযুক্ত অন্যতম পলাতক আসামি মেজর খালেদ ব্যাংককে ছিলেন। অপর পলাতক আসামি মেজর মুফাফফর ছিলেন ভারতে। ভারত থেকে এসে মেজর মুজাফফরও খালেদকে নিয়ে ব্যাংককে আমার সঙ্গে দেখা করেন। জিয়া হত্যার বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়। ওই হত্যাকাণ্ডের সঠিক তথ্য জানার ইচ্ছা আমার ছিল এবং সে রকম চেষ্টাও করি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আমি যা জেনেছি তা সংক্ষেপে এ রকম: মতি, মাহাবুব ও খালেদের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ২৪ ডিভিশনের জুনিয়র অফিসাররা জিওসি জেনারেল মঞ্জুরের অজান্তে প্রেসিডেন্ট জিয়াকে সার্কিট হাউস থেকে অপহরণ করে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জিয়াকে চাপ দিয়ে বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায়, বিশেষ করে সেনাপ্রধান এরশাদসহ অন্যান্য দুর্নীতিপরায়ণ সামরিক অফিসার এবং পাকিস্তানপন্থী শাহ আজিজ ও অন্য দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করানো। কারণ এরশাদের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের হয়রানি, বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের ঢালাওভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বদলি করাসহ সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের ব্যাপক দুর্নীতি নিয়ে জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভ ছিল। মূলত এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁদের ওই উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে।
‘বিদ্রোহের সেই রাতে বেশ ঝড় হচ্ছিল এবং জিয়া সার্কিট হাউসের দোতলায় ঘুমিয়ে ছিলেন। ভোর চারটার দিকে অফিসাররা অতর্কিতে সার্কিট হাউস আক্রমণ করেন। ওই আক্রমণের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল তাতে কোনো সৈনিক, জেসিও বা এনসিওকে সরাসরি জড়ানো হয়নি। জুনিয়র অফিসাররা নিজেরাই দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে প্রথমে সার্কিট হাউসে রকেট লঞ্চার নিক্ষেপ করেন। পরে এক গ্রুপ গুলি করতে করতে ঝড়ের বেগে সার্কিট হাউসে ঢুকে পড়ে। গুলির শব্দ শুনে জিয়া রুম থেকে বের হয়ে আসেন এবং কয়েকজন অফিসার তাঁকে ঘিরে দাঁড়ান। ওই সময় লে. কর্নেল মতিউর রহমান মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে ‘জিয়া কোথায়, জিয়া কোথায়’ বলে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে আসেন এবং পলকেই গজ খানেক সামনে থেকে তাঁর চায়নিজ স্টেনগানের এক ম্যাগাজিন (২৮টি) গুলি জিয়ার ওপর চালিয়ে দেন। অন্তত ২০টি বুলেট জিয়ার শরীরে বিদ্ধ হয় এবং পুরো শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যায়। উপস্থিত অন্য অফিসাররা ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হয়ে যান। তাঁরা কোনো গুলি ছোড়েননি। শুধু দু-একজন অফিসার ‘কী করছেন, কী করছেন’ বলে চিৎকার করে ওঠেন। কিন্তু ততক্ষণে প্রেসিডেন্ট জিয়া মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।
‘...থাইল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত থাকা অবস্থায় ঢাকায় এলে (১৯৯১ সালে) আমি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে মেজর খালেদ ও মুজাফফরের সঙ্গে আমার আলোচনা বিস্তারিতভাবে অবহিত করি। যেসব অফিসারের উপস্থিতিতে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে জেনারেল জিয়াকে হত্যা করা হয়, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মেজর খালেদ ও মেজর মুজাফফরই তখন জীবিত ছিলেন।...১৯৯৩ সালে খালেদ ব্যাংককে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান এবং তাঁর লাশ ঢাকায় পাঠানো হয়।
‘বস্তুত, ঘটনার পরদিন মঞ্জুরের সঙ্গে কথা হওয়ার পর আমি বুঝতে পারি, মঞ্জুর জিয়া হত্যার সঙ্গে জড়িত নন এবং পরে মেজর খালেদের কাছ থেকেও জানতে পারি যে আমার ধারণাই সঠিক।’
স্বামীর হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন পরেই এক প্রকাশ্য জনসভায় খালেদা জিয়া তাঁর স্বামীর হত্যাকাণ্ডে এরশাদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ তোলেন। খালেদার এই অভিযোগ ছবিটি আরও জটিল করে তোলে। ডিজিএফআই কি এই কনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের—মতি, খালেদ, মাহবুব, মুজাফফর—দলে কোনো উসকানিদাতা এজেন্ট ঢুকিয়ে দিয়ে এদের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের খেলাটি খেলেছে? তাদের কি জিয়াকে অপহরণ করায় মদদ দেওয়া হয়েছিল, যেখানে প্রথম থেকেই জিয়াকে হত্যা করার জন্য তাঁদের অজ্ঞাতসারে ‘এক পরিকল্পনার ভেতর আরেক পরিকল্পনা’ লুকিয়ে রাখা হয়?
আমি সাধারণত এ ধরনের অনুমানের দ্বারা চালিত হই না। তবে একজন সতর্ক ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গটি আমার কাছে উত্থাপন করেছিলেন। তিনি এ ইঙ্গিতও করেছিলেন যে ১৯৮১ সালে ডিজিএফআইয়ের ভেতর সক্রিয় থাকা তাঁর কিছু সহকর্মী একটি উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন, যাঁরা এই তত্ত্বকে কোনোভাবে সঠিক প্রমাণ করতে পারেন। সেই অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা আমার সঙ্গে যেসব তথ্য বিনিময় করেছেন, সেসবও খুব যত্ন করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংগ্রহ করা। তাই এই চিন্তাটিও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। উপরন্তু খালেদা জিয়া যে তাঁর স্বামীর হত্যাকাণ্ডের জন্য এরশাদকে দায়ী করেছেন, এ অভিযোগও ফেলে দেওয়া যায় না।
এসবের মানে কী? প্রশ্ন ওঠে, জিয়া হত্যাকাণ্ড, তাতে ইচ্ছাকৃতভাবে মঞ্জুরকে জড়ানো বা তাঁকে ‘খুনি’ হিসেবে প্রচার করা এবং সেনা হেফাজতে মঞ্জুরকে তড়িঘড়ি করে হত্যা করা—এর সবটাই কি ডিজিএফআইয়ের সাজানো অপারেশন ছিল? এটাই কি সত্য? আমরা তা জানি না। নিশ্চিতভাবেই, এটি সত্য হলে ইঙ্গিতগুলো বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এই শার্লক হোমস মার্কা রহস্যের জটও হয়তো খুলবে, যেভাবে অন্যান্য বহু উত্তরহীন প্রশ্নের জবাব মিলেছে।
২০০৬ সালে আমি যখন জেনারেল মইনের সঙ্গে বসি, তখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য প্রকাশিত হওয়ার পর পিপি বা প্রসিকিউটরের কোনো তদন্তকারী এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কি না? তিনি মুখ শুকনো করে হেসে জানান, ‘না’।
এরপর এই দীর্ঘ তদন্ত ও এরশাদের বিচারপ্রক্রিয়া আর কতকাল চলবে তা নিয়ে আমরা কথা বললাম। এরশাদ ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে সত্য বলার মতো কোনো নির্ভরযোগ্য সাক্ষী খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে রাজনৈতিক ও বিচারিক সদিচ্ছার অভাবকে কেন্দ্র করে আমাদের আলাপচারিতা চলল। আগেই যা ইঙ্গিত করা হয়েছে, মইন তাঁর বইটিতে বলেছেন যে এরশাদ ও তাঁর সহযোগীরা মঞ্জুর হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।
মঞ্জুর হত্যার বিচারে দীর্ঘসূত্রতা এবং ১৯৮১ সালের সেই দুই সপ্তাহের বিভীষিকাপূর্ণ বিচারের মধ্যকার তুলনা টানেন মইন। সেই বিচারে ১৩ জন কর্মকর্তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা সবাই ছিলেন মুক্তিবাহিনীর লড়াকু যোদ্ধা। জিয়া হত্যাকাণ্ডের মাত্র এক মাস পর তাঁদের এই ‘এক্সপ্রেস’ ফিল্ড কোর্ট মার্শাল সব দিক থেকেই তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল দেখায়। এমনকি মিলিটারি কোড অব জাস্টিসে আত্মপক্ষ সমর্থনের যে সুযোগ দেওয়া আছে, তা-ও অগ্রাহ্য করা হয়।
তদুপরি অমানুষিক নির্যাতন করে তাঁদের সবাইকে সেই ‘মিথ্যা আখ্যান’ স্বীকার করতে বাধ্য করা হয় যে তাঁরাও মঞ্জুরের মতো জিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেছেন। স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য তাঁদের প্রহার করা হয়, আঙুল থেকে নখ উপড়ে ফেলা হয়, যৌনাঙ্গ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। জুলফিকার আলী মানিক এই তথাকথিত বিচারের ওপর লেখা তাঁর সাহসী বইটিতে এসব ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তুলে ধরেছেন। শারীরিকভাবে নিপীড়ন করা সত্ত্বেও এই কর্মকর্তাদের ফিল্ড কোর্ট মার্শালে হাজির করা হলে তাঁরা সাহসিকতা ও ক্ষোভের সঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের অভিসম্পাত করেন।
আবারও প্রমাণিত হলো যে সরকারি কৌঁসুলি ও তদন্তকারীরা মইনের বইয়ে যেসব ইঙ্গিতপূর্ণ দিক রয়েছে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, যেটা তাঁদের দায়িত্ব ছিল।
প্রসিকিউটর ও সাংবাদিকের লক্ষ্য অনেকটা একই, সত্যানুসন্ধান করা। সব পেশার মতো এখানেও কেউ কাজটি ভালোভাবে করেন, কেউ বাজেভাবে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে একটি আর্থিকভাবে সচ্ছল, সুসংগঠিত ও স্থির লক্ষ্য প্রসিকিউশন দল বাংলাদেশে অনেক বাধার সম্মুখীন হবে। বিশেষত, যেসব একদা ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তারা তদন্ত করছে তাঁদের তরফ থেকে মৃত্যুর হুমকি আসাও কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। তার পরও চট্টগ্রামের অস্ত্র মামলার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, এই ব্যবস্থার মধ্যেও গুরুতর অপরাধের বিরুদ্ধে ধৈর্যশীল তদন্ত করার সক্ষমতা এখানে রয়েছে। এমনকি তা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও। এর জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ও বিচারিক সদিচ্ছা।
মঞ্জুর-হত্যাকাণ্ডের এক প্রত্যক্ষদর্শী
জেনারেল মইনের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর কাছে আমি একটি গোপন তথ্য প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিই। বাংলাদেশের বাইরে এক সোর্সের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। খুবই নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছিল তাঁকে। নিজেকে তিনি চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে সংঘটিত মঞ্জুর হত্যাকাণ্ডের একজন সাক্ষী হিসেবে দাবি করেন।
বাকী অংশ পড়তে ক্লিক করুন