মেজর জেনারেল আবুল মঞ্জুর হত্যাকাণ্ড: নেপথ্য কাহিনির দ্বিতীয় পর্ব—৪
খুনিরা নেমেছিল এরশাদের নেতৃত্বে
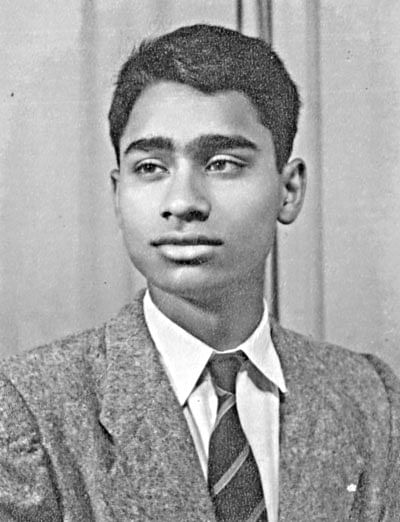
মঞ্জুর হত্যাকাণ্ড বিষয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের এই প্রকাশমান রচনায় ১৯৯৫ সালে দেওয়া কয়েকজন সৈনিক ও পুলিশ কর্মকর্তার হলফনামা বর্ণনা ও পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। যে ঐতিহাসিক পটভূমিতে অ্যাটর্নি জেনারেল আমিনুল হক ও সিআইডির তৎপরতায় এসব সংগৃহীত হয়েছে, তা-ও যাচাইবাছাই করা হয়েছে।
এ রচনার শুরুতেই বলা হয়েছে, আমাদের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত ও এই রচনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিল হলো উভয় ক্ষেত্রেই ঊর্ধ্বতন কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তার নাম উঠে এসেছে, যাঁরা একটি ‘বিশেষ অভিযান’ চালিয়ে মঞ্জুরকে হত্যা করতে ভূমিকা পালন করেন।
প্রথম আলোর একজন জ্যেষ্ঠ সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ এই মিলকে বর্ণনা করেছেন এভাবে: ‘সকল পথই রোমের দিকে যায়।’ অর্থাৎ, সৈনিকদের সাক্ষ্য ও পৃথকভাবে নেওয়া স্বতন্ত্র দুটো সূত্রেরই (লরেন্স লিফশুলৎজ ও জিয়াউদ্দীন চৌধুরী) ভাষ্য অনুসারে, মঞ্জুর হত্যার পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে সেনাবাহিনীর একেবারে ‘ওপরের নির্দেশে’।
তবে ঘটনার এ দুই ভাষ্যের মধ্যে কিছু গরমিলও আছে। এই গরমিলটি দেখা যাচ্ছে জেনারেল মঞ্জুরের জীবনের শেষ মুহূর্তের কিছু বিবরণে।
ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত বিবরণে দেখা যাচ্ছে, জিয়াউদ্দীনের সূত্র এবং তাঁর বই প্রকাশের বহু আগে সাক্ষাৎকার নেওয়া আমার স্বতন্ত্র সূত্র—উভয়ের বর্ণনাতেই দেখা যাচ্ছে মঞ্জুর একজন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মকর্তার হাতে নিহত হয়েছেন। মঞ্জুরকে যে কক্ষে আটকে রাখা হয়েছিল কর্মকর্তাটি সেখানে ঢোকেন এবং কিছুক্ষণ পরই তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন। এরপর হত্যাকারী বিনা প্রতিরোধে সেনানিবাস ছেড়ে বেরিয়ে যান।
এ দফার লেখাটি আমরা লিখছি পাঁচজন সৈনিকের দেওয়া হলফনামার ওপর ভিত্তি করে। এসব নথি আমাদের হাতে আসামাত্র মঞ্জুর হত্যার ভিন্নতর এই বিবরণটি প্রকাশ করা সাংবাদিক হিসেবে আমার এবং পত্রিকা হিসেবে প্রথম আলোর কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এটি করতে না পারলে তা দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ হতো। ডেইলি স্টার-এর ওপরও এ দায়িত্ব বর্তায়, কারণ তারাও ফেব্রুয়ারি মাসে আমার প্রথম রচনাটি প্রকাশ করে।
মঞ্জুর কার হাতে খুন হয়েছেন, এই দুই বিবরণের মধ্যে মূল পার্থক্য সেটিকে কেন্দ্র করে। এই পাঁচজন সৈনিক দাবি করেছেন, ‘ওপরের নির্দেশে’ তাঁদের মধ্যে একজন মঞ্জুরকে হত্যা করেছেন। এমনকি যে কর্মকর্তা তাঁদের এ নির্দেশটি দেন, এমনকি তখনো যাঁরা ফায়ারিং রেঞ্জে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নামও তাঁরা উল্লেখ করেছেন।
প্রশ্ন হলো, জেনারেল মঞ্জুরের শেষ মুহূর্তের কোন বিবরণটি সঠিক? এর বাইরেও কি এমন আর কোনো বিবরণ আছে, যা আমরা জানি না?
সৈনিকদের হলফনামায় কী কোনো পরিবর্তন ঘটেছে? তাঁদের কি অনেকগুলো খসড়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে? প্রাথমিকভাবে কি সৈন্যদের নিজেদের নাম জড়াতে এবং তাঁদের মধ্যে কারও ওপর ‘দায়িত্ব’ সম্পন্ন করার দায় চাপাতে চাপ দেওয়া হয়েছে? তাঁরা একজন ব্যক্তির নাম বলেছেন, কিন্তু তিনি কোথাও নেই।
যেসব নথিপত্র আমাদের হাতে এসেছে, তাতে কোথাও তাঁকে গ্রেপ্তার দেখা যায় না। যে সৈনিকটি মঞ্জুরকে গুলি করেছেন বলে অভিযোগ উঠছে, আমিনুল হক ১৯৯০ সালে তদন্ত শুরু করার অনেক আগেই হয়তো তিনি দেশ ত্যাগ করেছেন কিংবা সে সুযোগ তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই।
কিংবা প্রধান কৌঁসুলি ও সিআইডি হয়তো সৈন্যদের মধ্যে এই বোধ সৃষ্টি করেছিলেন যে কাদের নির্দেশ মেনে তাঁরা কাজটি করেছিলেন,
তা না বললে এই হত্যাকাণ্ডে মাত্রা অনুযায়ী তাঁদের শাস্তি ভোগ করতে হবে? এর ভিত্তিতেই কি সেদিন তাঁদের ফায়ারিং রেঞ্জে উপস্থিত ‘চেইন অব কমান্ড’-এর সেসব কর্মকর্তার নাম উল্লেখ করতে বলা হয়েছিল, যাঁরা তারও আগে এই সৈনিকদের ১ জুন একটি ‘বিশেষ অপারেশন’-এ অন্তর্ভুক্ত করেন, যার সমাপ্তি ঘটে মঞ্জুরকে হত্যার মধ্য দিয়ে?
সৈনিকেরা কি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁদের একজনকে দিয়ে খুনটি করিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাঁদের ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, যাতে ওপর মহলের কারও গায়ে কোনো কাদা না লাগে কিংবা মানুষের চোখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যায়? এ ঘটনার সঙ্গে যে সেনাবাহিনীর ওপরের মহল জড়িত, আমিনুল হক তা মনে করতেন।
পরের দিন ২ জুন ‘উচ্ছৃঙ্খল সৈন্য’দের হাতে মঞ্জুরের নিহত হওয়ার গুজব ছড়ানোর ব্যাপারটিও কি এই ‘বিশদ পরিকল্পনা’র অংশ ছিল? সিআইডি ও আমিনুল হক কি হাটহাজারী অপারেশনে থাকা সৈন্যদের এ কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন? এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে এ প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।
এটা কি সম্ভব যে মঞ্জুর তাঁকে আটকে রাখা সেই ভিআইপি গেস্টহাউসে ঢাকা থেকে আসা একজন ঊর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তার হাতেই খুন হয়েছেন? এরপর কি লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামস (পুরো নাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামসুর রহমান শামস) তাঁর মৃতদেহ সিএমএইচে নিয়ে যান? মঞ্জুরের মৃতদেহের ময়নাতদন্ত যিনি করেছিলেন সেই সামরিক চিকিৎসক কর্নেল এ জেড তোফায়েলের ভাষ্য অনুযায়ী, লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামস জেনারেল মঞ্জুরের ‘মৃতদেহ শনাক্ত করেন’ ও সিএমএইচের কর্তব্যরত কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করেন।
মঞ্জুরের মৃতদেহ সিএমএইচে নিয়ে আসতে সৈনিকেরা কী শামসকে সহযোগিতা করেছেন? ফায়ারিং রেঞ্জের ঘটনাটি কি সেই ঢাকা থেকে আসা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বাঁচানোর জন্য সাজানো হয়েছিল, যিনি মঞ্জুরের কক্ষে ঢুকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করেন? নাকি মঞ্জুরকে ফায়ারিং রেঞ্জেই হত্যা করা হয়, একজন সৈন্য তাঁকে গুলি করেন, যখন আরও কয়েকজন সৈনিক ও কর্মকর্তা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন?
আমরা যা জানি, তাহলো বহু প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা। সিআইডির মতো একটি সংস্থা ঘটনার তদন্ত করার মানে হলো, প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। সত্যানুসন্ধানী সাংবাদিকদের ক্ষেত্রেও কথাটা প্রযোজ্য।
দুজনের উপায় তাই বলে এক রকম নয়, তবে ন্যূনতম সততা থাকলে লক্ষ্য নির্ঘাত এক হতে বাধ্য। লক্ষ্য হলো, সত্য উদ্ঘাটন করা। আশার কথা হচ্ছে, যথাযথ তথ্যই অপরাধীকে ধরার মূল অস্ত্র।
সব তদন্তের ক্ষেত্রেই একই ঘটনার ভিন্নধর্মী, কখনো কখনো পরস্পরবিরোধী দুটো রূপ সামনে এসে হাজির হয়। তদন্তকারীদের দক্ষতা ও বিচার বিভাগ এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে কী রকম সহযোগিতা দেয়, তার ওপর নির্ভর করে অপরাধীদের শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব কি না।
এ পরিস্থিতির সঙ্গে রাশোমন চলচ্চিত্রটির একটি পটভূমিগত মিল রয়েছে। কিংবদন্তি জাপানি চলচ্চিত্রকার আকিরা কুরোসাওয়া ১৯৫০ সালে এ ছবিটি মুক্তি দেন। সত্যজিৎ রায় যেমন ভারতবর্ষে, কুরোসাওয়া ঠিক একইভাবে জাপানে সমাদৃত। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুরোসাওয়া আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান, শুধু এর মানের জন্য নয়, মানব জীবনের এক অসহনীয় উভয়সংকটকে চিত্রায়িত করার জন্যও। মঞ্জুর হত্যা মামলায়ও রাশোমন ছবির একটি মাত্রা রয়েছে। এটি আমাদের এই উভয়সংকটকে মোকাবিলা করতে সাহায্য করতে পারে।
রাশোমন ছবিটি নির্মিত হয়েছে দ্বাদশ শতকের জাপানের প্রেক্ষাপটে। ছবিটিতে এক সামুরাই যোদ্ধার হত্যাকাণ্ডের গল্প বলা হয়েছে। তিনি কিয়োতো শহরের কাছাকাছি এক দুর্গম অরণ্য দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের জীবিত সাক্ষী মাত্র তিনজন: মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, একজন ডাকাত ও একজন কাঠুরে। গল্পটির বয়ানের একপর্যায়ে নিহত সামুরাই নিজেও অশরীরী আত্মা হিসেবে হাজির হয়ে আদালতে নিজের মৃত্যুর ঘটনার বিবরণ দেয়। ছবিতে সামুরাই তাই চতুর্থ সাক্ষী হিসেবে হাজির হন।
কিন্তু প্রত্যেক সাক্ষী এই হত্যাকাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেন। গল্পটা শুরু হয় এভাবে: একজন ভিক্ষু ও একজন কাঠুরে কিয়োতো শহরের প্রধান ফটকের নিচে উপবিষ্ট, যার নাম ‘রাশোমন তোরণ’। তুমুল ধারাপাত হচ্ছে। তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন ফটকটির নিচে। তাঁরা দুজনই এই হত্যাকাণ্ডটি নিয়ে কথা বলছেন। তাঁদের দুজনকেই আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা হয়েছে।
সামুরাই ও তাঁর স্ত্রী পথ দিয়ে যাওয়ার সময় এই ভিক্ষু তাঁদের পার হয়ে গিয়েছিলেন। কাঠুরে সামুরাইয়ের মৃতদেহের খোঁজ পেয়ে সঙ্গে
সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে কর্তৃপক্ষকে জানান। আরও পরে কাঠুরে ভিক্ষুর কাছে স্বীকার করেন, সামুরাই খুন হওয়া পর্যন্ত পুরো ঘটনাটি তিনি অরণ্যের ভেতর থেকে দেখেছেন। কিন্তু তিনি আদালতের কাছে সে কথা বলেননি, পাছে কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে যান।
কিন্তু সত্য কথাটি আসলে কে বলছেন, সেটা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না। প্রত্যেকে নিজেরা যা দেখেছেন, তাঁর তাঁর মতো করে সে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন। জাপানি ভিক্ষু বুঝতে চেষ্টা করছেন, কে সত্য কথাটা বলছে। ছবিটির মর্ম এখানেই যে ভিক্ষু শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারেন, সত্য কথাটি কে বলছে এবং কেন। এই অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করার কারণেই ভিক্ষু মানবতার ওপর বিশ্বাস ফিরে পান।
রাশোমন এখন চট্টগ্রামের রাস্তায়। এর রহস্যের উপস্থিতি বাংলাদেশের আদালতের পরিসরে অনুভূত হচ্ছে। কোনো সন্দেহ নেই, একজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার শিকার সেই ব্যক্তিটি ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ যোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক। লেখক সৈয়দ বদরুল আহসান উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মঞ্জুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বলেছেন, ‘খুন, জঘন্যতম খুন’।
রাশোমন ছবিটির মতো এই মামলার সাক্ষীদের সাক্ষ্যেও বিদ্যমান অমিলগুলোর মধ্যে কিছু মিল রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, জেনারেল মঞ্জুর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, এই পূর্বনির্ধারিত হত্যাকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন উচ্চপর্যায়ের সেনা কর্মকর্তারা। আর তাতে হত্যাকাণ্ডের অপরাধ আরও ভারী হয়ে ওঠে। এখন প্রশ্ন হলো, মঞ্জুরকে কে খুন করেছেন? একজন সৈনিক, একজন মেজর জেনারেল, নাকি আর কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা? এর উত্তর আমরা জানি না।
এ ছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে আছে, সেনাবাহিনীর কোন ব্যক্তি বা দল এ হত্যা অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছে? অধিকতর তদন্তের মাধ্যমেই এসব জিজ্ঞাসার সুরাহা করা সম্ভব। এ মামলায় আরও যাঁরা সাক্ষী দিতে পারেন, যাঁদের কথা এখনো শোনা সম্ভবপর হয়নি, অনুকূল পরিবেশ পেলে তাঁরাও হয়তো সাক্ষ্য দেবেন।
এ কথাটি উপলব্ধি করতে হবে যে জেনারেল মঞ্জুরের হত্যাকাণ্ড একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি বড়
ধরনের পালাবদল ঘটে গেছে। যে সেনাবাহিনী মুক্তিযুদ্ধ-ফেরত যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল, ১৯৮১ সালে তা পাকিস্তানের সহযোগী বা যুদ্ধের সময় কোনো পক্ষ না নেওয়া লোকদের হাতে চলে যায়। কোনো পক্ষ না নেওয়া এই লোকগুলো দেশের সবচেয়ে ক্রান্তিলগ্নে দেশমাতৃকাকে রক্ষা করার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেননি। অথচ এই মুক্তিযোদ্ধা সৈনিকেরা পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করেছেন।
জেনারেল মইনের দৃষ্টিতে মঞ্জুর কোনো অভ্যুত্থান করেননি। জেনারেল এরশাদ ও ঘনিষ্ঠরা একটি দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনার শেষ প্রান্তে অবস্থান করছিলেন, যার মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে পাকিস্তান-ফেরত সেনা কর্মকর্তারা সেনাবাহিনীতে তাঁদের কর্তৃত্ব নিরঙ্কুশ করার পথে এগোচ্ছিলেন। একসময় অস্পৃশ্য হলেও তাঁরা এখন নিজেদের হাতে কর্তৃত্ব নিয়ে নেন ও নিষ্ঠুরভাবে সেনাবাহিনী থেকে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের হটিয়ে দেন। আর এসব কিছু আকস্মিকভাবে হয়নি।
কোনো সন্দেহ নেই, বছরের পর বছর ধরে জিয়া হত্যাকাণ্ডে মঞ্জুরকে জড়িয়ে অনেক মিথ্যা অপবাদ বাজারে ছড়ানো হয়েছে। অথচ একটি প্রমাণও কেউ দাখিল করতে পারেনি। তার পরও জেনারেল এরশাদ ও তাঁর সহযোগীরা নিজেদের বিচারকের আসনে বসিয়ে দেন। জিয়াউদ্দীনের সেনানিবাস-সূত্র যথার্থ তথ্য দিয়ে থাকলে এবং ১ জুন ‘বিশেষ অভিযান’-এ অংশ নেওয়া সৈনিকেরা সত্য বলে থাকলে সেনাবাহিনীর ‘ওপরের মহল’ জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে হন্তারকের ভূমিকায় নেমেছিল। জেনারেল মঞ্জুরের খুন তেমন একটি বিশদ অভিযানেরই অংশ।
এর পরের কয়েক মাসে সেনা কর্তৃপক্ষ নির্দ্বিধায় ক্যাঙারু কোর্টে ‘দ্রুত’ ফিল্ড মার্শাল কোর্ট বসিয়ে বহু কর্মকর্তা ও সৈনিককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেয়। এর আগে নির্যাতন করে তাঁদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নেওয়া হয়। অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাশ দেওয়া হয়নি। সেটি ছিল তেমন একটি দ্রুতগামী ট্রেন, যার একটিই মাত্র গন্তব্য ছিল।