রজতজয়ন্তীর বিশেষ লেখা
প্রতিস্থাপন পর্যায়ে প্রজনন হার অর্জনের পথে বাংলাদেশ
মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল সম্পদে অপ্রতুল একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসেবে। কিন্তু নিন্দুকদের আশঙ্কা অসত্য প্রমাণ করে একের পর এক বাধা পেরিয়ে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। এই এগিয়ে যাওয়ার পথ রচিত হয়েছিল কিছু অভূতপূর্ব ঘটনা, অভিনব ভাবনা, ভবিষ্যৎমুখী পরিকল্পনা ও উদ্যোগে। আমরা ফিরে দেখছি বাংলাদেশের উজ্জ্বল সেসব মুহূর্ত।
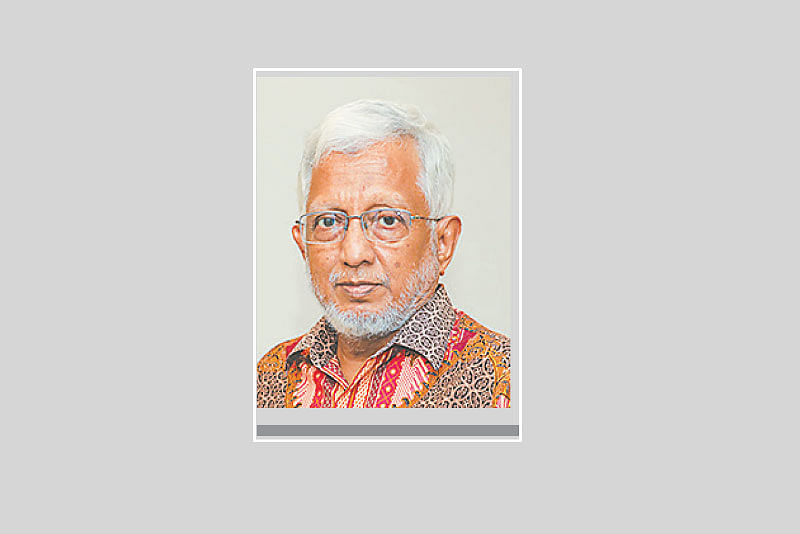
১৯৬০–এর দশকে অপরিকল্পিত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইয়ুব খান সরকার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলে একই কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের দিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সাড়ে ৬ কোটি। জাতিসংঘের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ইউএনএফপিএর প্রতিবেদনে দেখা যায়, বর্তমানে পাকিস্তানের জনসংখ্যা প্রায় ২৩ কোটি (বিশ্বে পঞ্চম) এবং বাংলাদেশের ১৭ কোটি (বিশ্বে অষ্টম)। এই তুলনা থেকে বোঝা যায়, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ জনসংখ্যা সীমিত রাখতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।
এই উপমহাদেশ সব সময় ঘনবসতিপূর্ণ ছিল। ১৬১৭ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে ৩ লাখ। মোগলরা চলে যাওয়ার পর ব্রিটিশদের আগমনের শুরুর দিকে ঢাকার জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৬৮ হাজার। দেশভাগের আগে, আমাদের দেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের যে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছিল, সেখানে জনসংখ্যা ছিল ৪ কোটির একটু বেশি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের একটা অংশ কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে পাড়ি জমায়। সে অনুপাতে মুসলিম জনগণ এ দেশে খুব একটা আসেনি।
হিন্দুধর্মাবলম্বীদের অনেকে চলে যাওয়ার পর জনসংখ্যা আবার বাড়তে শুরু করে। ১৯৫২-৫৩ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত হাজারে ৩০-৩৫ জনের জন্ম হতো এবং প্রায় ২০–এর কাছাকাছি মারা যেত। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১ দশমিক ৫। ১৯৪০–এর দশকের শুরুর দিকে অ্যান্টিবায়োটিকের বাণিজ্যিক ব্যবহার শুরু হয়। এর কল্যাণে মানুষ জীবাণুঘটিত বিভিন্ন রোগে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।
অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার, ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচি যুগপৎভাবে চলতে থাকায় মৃত্যুহার কমতে থাকে। কিন্তু জন্মহার থাকে অপরিবর্তিত। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা ১৯৬১ সাল থেকে চলতে থাকে। যে কারণে ১৯৪৭ সালের জনসংখ্যা ১৯৭১ সালে হয়ে যায় দ্বিগুণ।
মুক্তিযুদ্ধের পরপর ঢাকা শহরের জনসংখ্যা ছিল ১০ লাখের কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হারের ভিত্তিতে আমরা বলি, যুদ্ধের শুরুতে জনংখ্যা ছিল সাড়ে ৭ কোটি। ১৯৮১ সালের জনশুমারিতে দেখা যায়, জনসংখ্যা প্রায় ৯ কোটিতে উঠে গেছে। অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যেসব সমস্যা হতে পারে, এসব উদ্বেগ থেকে এর সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৫০-এর দশক থেকেই অপরিকল্পিত গর্ভধারণ রোধ করার চেষ্টা পৃথিবীব্যাপী শুরু হয়।
সেই চিন্তাভাবনা থেকেই আইয়ুব খান সরকারের উদ্যোগে ১৯৬১ সালে দেশের মানুষের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে প্রচার শুরু করা হয়। যদিও এর আগে ১৯৫৩ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে বেসরকারিভাবে ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অব পাকিস্তান স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন ক্লিনিক থেকে কনডম, খাওয়ার বড়ি বিতরণ করত। খাওয়ার বড়ি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকার কারণে প্লাস্টিকের তৈরি ইনট্রা ইউটেরিয়ান ডিভাইস (আইইউডি) উন্নত বিশ্বের নারীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। আমাদের দেশেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করার পাশাপাশি কনডম এবং খাওয়ার বড়ি ব্যবহার করা হতো।
পরিবার পরিকল্পনার ধারণাটি দেশের মানুষের মধ্যে পরিচিতি লাভ করার পর ১৯৬০-১৯৬৫ সালের মধ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মহকুমা ও থানাপর্যায়ে কিছু ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। থানা পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে প্রত্যেককে দেওয়া হয় একটি করে জিপ গাড়ি এবং গ্রামাঞ্চলে প্রচারের জন্য অডিও–ভিজ্যুয়াল (এভি) ভ্যান। পাশাপাশি প্যারামেডিক নিয়োগ দেওয়া হয় আইইউডি স্থাপনে সহায়তা করার জন্য। ইউএসএআইডির আর্থিক সহায়তায় এই কর্মসূচি পাকিস্তান সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে কিছু জনবল নিয়োগ করা হয়। যাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতেন পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য। কর্মসূচির প্রাথমিক পর্যায়ে খাবার বড়ি, কনডম, আইইউডি। এর মধ্যে উনসত্তরের গণ–অভ্যুত্থান থেকে ১৯৭১ সালের সময়টাতে এসব নিয়ে তেমন অগ্রগতি হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই কর্মসূচি অত্যন্ত দৃড়ভাবে চালু করেন। ওদিকে পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টো এই কর্মসূচি বন্ধ করে দেন।
১৯৭৪ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে জনসংখ্যা নীতি তৈরি করা হয়, যা ঘোষণা করা হয় ১৯৭৬ সালের দিকে। স্বাধীন দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জনসংখ্যা ১০ কোটির মধ্যে স্থির রাখার সুপারিশ করা হয় এবং মোট প্রজনন হার (টিএফআর) ২০০০ সালের মধ্যে নামিয়ে আনতে হবে দুইয়ে। সত্তরের দশকে জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি শতকরা ৫ থেকে ৭ জন গ্রহণ করতেন। স্বাধীনতার আইসিডিডিআরবি কুমিল্লার মতলবে মাঠপর্যায়ে মুখে খাওয়ার বড়ি ও ইনজেকশন বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিয়ে দেখতে পায়, দুই বছরের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার ২০-২২ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব।
আমাদের প্রথম জনসংখ্যানীতিতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়, দেশের নিট রিপ্রডাক্টিভ রেট ২০০০ সালের মধ্যে ১ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সরকার মাঠপর্যায়ে প্রায় ১০ হাজার কর্মী নিয়োগ করে আইসিডিডিআরবি-এর পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে। প্রতিটি ইউনিয়নে একজন পুরুষ এবং তিনজন নারী কর্মী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে ইউনিয়নের ক্লিনিক থেকে সেবা দিতে শুরু করলে টিএফআর ৬ থেকে চারে নেমে আসে।
১৯৮৪ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে কর্মসূচি আরও জোরদার করা হলে ইউনিয়নভিত্তিক না গিয়ে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সেবাদানের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। কারণ, ইউনিয়ন ভিত্তিতে দেখা যায় কোনো ইউনিয়নে জনসংখ্যা ৫০ হাজার, আবার কোনো ইউনিয়নে ১০ হাজার। হিসাব করে দেখা যায়, ৬ হাজার মানুষের জন্য গড়ে একজন কর্মীর মাধ্যমে দুই মাস অন্তর একজন সেবাগ্রহীতাকে সেবা দেওয়া সম্ভব।
প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষকে স্টেরিলাইজেশন অর্থাৎ স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হতো। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে স্থায়ী পদ্ধতিতে জোর দেওয়া হলে ১৯৮৬ সালের দিকে ৯ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে ৫ লাখের বেশি মানুষ এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন। অথচ আজকের ১৭ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে বছরে ২ লাখ মানুষও এটা গ্রহণ করেন না। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে কর্মী এবং সেবাগ্রহীতাকে নগদ পয়সা, শাড়ি, লুঙ্গি—এসব প্রণোদনা দেওয়া হতো। প্রণোদনার লোভে বয়স গোপন করে ১৬ বছরের তরুণ কিংবা ৭০ বছরের বৃদ্ধ এই পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাই এই কর্মসূচি নিয়ে সমালোচনাও হয় অনেক। সমালোচনার পর সরকার একটু শক্ত অবস্থান নেয় এবং নারী কর্মীরা তখন বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাওয়ার বড়ি ও ইনজেকশনের প্রচার শুরু করেন।
দেশের রেডিও–টেলিভিশনসহ বিভিন্ন জায়গায় মায়াবড়ি নামক খাওয়ার বড়ির ব্যাপক প্রচার শুরু হয়। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে বরাবরই নারীরা এগিয়ে এসেছেন। এখানে পুরুষের অংশগ্রহণ খুব কম, তাঁরা কনডম কম ব্যবহার করেন, স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করেন না। তখন আইইডি ৫ থেকে ৭ বছর পর্যন্ত নিশ্চয়তা দিত। কপার টি-৩০০ এখন ১৫ বছর পর্যন্ত নিশ্চয়তা দেয়। এসবের সুবিধা সম্পর্কে আমরা প্রচারণা চালানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু মানুষ তেমন সাড়া দেয়নি। বাড়িতে বাড়িতে সরকার বিনা মূল্যে খাওয়ার বড়ি বিতরণ করতে শুরু করল। এর সঙ্গে তিন মাস মেয়াদি ইনজেকশনও দেওয়া হতো।
১৯৯০ সালের দিকে দেশের টিএফআর কমে সাড়ে তিনে নেমে আসে। তারপর ২০০০ সালের দিকে ২ দশমিক ৪৫ এবং এখন ২ দশমিক ২২। আমি ১৯৯০ সালে পাকিস্তানে পপুলেশন কাউন্সিলের অফিসে যোগ দিয়ে দেখি, সেখানে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির সেবা গ্রহণের হার ৬-৭ শতাংশ। আমাদের দেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির সাফল্যে তারা অবাক হয়ে যায়। আমাদের দেশের কর্মকৌশল তাদের দেশে বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তাদের রাজনৈতিক অনৈক্যের কারণে তা আর সফল হতে পারেনি। ফলে তাদের জনসংখ্যা চলে যায় ২৪ কোটির কাছাকাছি।
আমরা আরও আগে থেকে সচেতন হলে জনসংখ্যা ১৫ কোটির মধ্যে ধরে রাখা যেত। যেটা কোরিয়া, থাইল্যান্ড করেছে। কিন্তু আমাদের জনসংখ্যা ২০৫০ সালের দিকে ২০ কোটির কাছাকাছি গিয়ে স্থির হবে এবং এর ১০-১২ বছর পর থেকে কমতে থাকবে। কতটা কমবে, তা মানুষের আচরণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করবে। আমাদের দেশে প্রতি ১০০ জন সক্ষম দম্পতির মধ্যে ৬০ জন জন্মবিরতিকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। প্রজননহার প্রতিস্থাপন পর্যায়ে পৌঁছাতে হলে তা ৭০–এর কাছাকাছি হতে হবে। কিন্তু এটা তো জোর করে বাড়ানো যায় না। ১৯৭২ সালে ওয়ার্ল্ড ক্রাইম রিলেটেড ইনসিডেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বেশ কিছু মাকে গর্ভাবস্থায় পাওয়া গেছে। তখন প্রযুক্তি ব্যবহার করে গর্ভপাত করার বৈধতা দেওয়া হয়। পরে আমাদের দেশে ১৯৭৪ সালে এমআর অর্থাৎ মাসিক নিয়মিতকরণ পদ্ধতি বৈধ করা হয়। গর্ভপাত আমাদের দেশে এখনো অবৈধ, কিন্তু এমআর বৈধ। মাসিক অনিয়মিত হলে ৮ সপ্তাহের মধ্যে একজন এফডব্লিউভি হিসেবে পরিচিত নারী প্যারামেডিকের মাধ্যমে এবং ৮ সপ্তাহের ওপরে ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত একজন চিকিৎসকের মাধ্যমে এমআর করা যায়। আমাদের দেশে ৪৫-৫০ লাখ নারী গর্ভধারণ করেন এবং ২৮ থেকে ৩০ লাখ শিশুর জন্ম দেন। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে প্রতিবছর এমআর হয় ১৫-২০ লাখ।
দেশের প্রায় দেড় কোটি সক্ষম পুরুষ দেশের বাইরে আছেন। এর মধ্যে ৭৫ লাখ বিবাহিত। তাঁরা যে তিন থেকে চার বছর দেশের বাইরে থাকেন, এটাকে আমরা পত্নীবিচ্ছেদ বলি। এই চার বছর তাঁরা যদি স্ত্রীর সঙ্গে থাকতেন, তাহলে তাঁদের পরিবারে সন্তান আসত, পরের বছর হয়তো আরেকটি। অর্থাৎ এখানে একটি ধারাবাহিকতায় বিচ্ছেদ তৈরি হচ্ছে। সেটা নিয়ে আমরা কোনো গবেষণা করছি না। কিন্তু এটাও জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত একটি বিষয়। এসবের সংমিশ্রণে টিএফআর হয় ২ দশমিক ৩ বা ২ দশমিক ২–এর কাছাকাছি আসে।
জনসংখ্যার কার্যক্রমের বেলায় আমাদের তুলনা করা হয় পাকিস্তান ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে কম আছি, পাকিস্তানের চেয়ে ওপরে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গে ৫০ শতাংশ মানুষ স্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহার করেন। কিন্তু আমাদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাওয়ার বড়ি গ্রহণ করেন ৫০ শতাংশ। বাকি ৫০ শতাংশ বাকি পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করেন। তা সত্ত্বেও আমরা প্রতিস্থাপন পর্যায়ের প্রজননহার অর্জনের কাছাকাছি আছি।
ওবায়দুর রব:জনসংখ্যাবিশেষজ্ঞ