রজতজয়ন্তীর বিশেষ লেখা
যুগান্তকারী নীতিতে ওষুধশিল্পের বিকাশ
মুক্তিযুদ্ধের পর আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল সম্পদে অপ্রতুল একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসেবে। কিন্তু নিন্দুকদের আশঙ্কা অসত্য প্রমাণ করে একের পর এক বাধা পেরিয়ে এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। এই এগিয়ে যাওয়ার পথ রচিত হয়েছিল কিছু অভূতপূর্ব ঘটনা, অভিনব ভাবনা, ভবিষ্যৎমুখী পরিকল্পনা ও উদ্যোগে। আমরা ফিরে দেখছি বাংলাদেশের উজ্জ্বল সেসব মুহূর্ত।
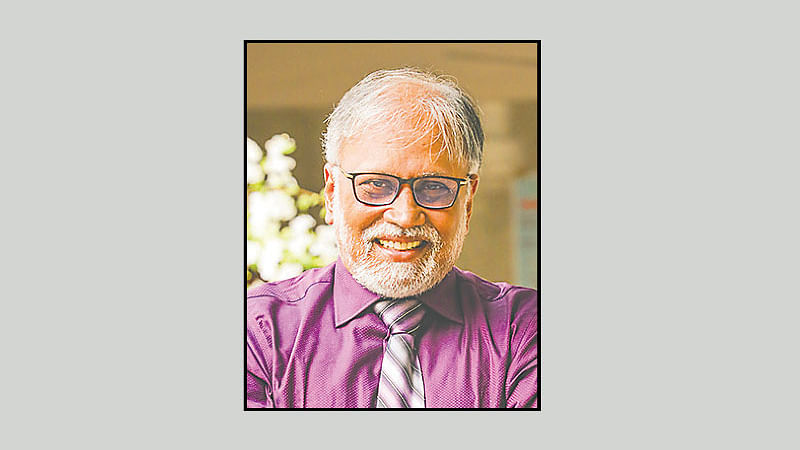
রোগের বিরুদ্ধে মানুষের দীর্ঘদিনের লড়াইয়ে বেঁচে থাকার তাগিদের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার মিশ্রণে আবিষ্কৃত উপাদানগুলোই পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধ হয়ে ওঠে। রোগ নিরাময়ের মাধ্যম হিসেবে ওষুধের কোনো বিকল্প বিজ্ঞানের দূরদিগন্তেও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। ফলে ওষুধ এখনো চিকিৎসাবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় চরিত্র। স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ওষুধের গুরুত্ব বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ওষুধকে স্বাস্থ্য খাতের ছয়টি অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামোর অন্যতম বলে ঘোষণা করেছে। ফলে ওষুধের প্রাপ্যতা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনের অন্যতম নিয়ামক।
ওষুধ বরাবরই একটি নিয়ন্ত্রিত পণ্য, এমনকি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের উপস্থিতিও প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো। ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপনের পাশাপাশি তাদের চিকিৎসাপদ্ধতিও প্রবর্তন করে, যার প্রধান অনুষঙ্গ পশ্চিমা ওষুধ। পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল যেমন মিসর, চীনের মতো আমাদেরও ছিল স্থানীয় ওষুধের শক্তিশালী ঐতিহ্য। কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পশ্চিমের একাধিপত্যের কারণে আমাদের হাজার বছরের স্বীকৃত ও শক্তিশালী ওষুধের জ্ঞান তার প্রভাব হারিয়ে ফেলে। এই অঞ্চলে প্রথম ওষুধসংক্রান্ত আইন প্রণীত হয় ‘পয়জনস অ্যাক্ট ১৯১৯’ এবং তারপর পর্যায়ক্রমে ‘ডেঞ্জারাস ড্রাগ অ্যাক্ট ১৯৩০’ এবং ‘ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট ১৯৪০’।
২৫ বছরের পাকিস্তান শাসনামলে ওষুধ–সম্পর্কিত কোনো আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১৯৫০–এর দশক থেকে পাকিস্তানে কিছু দেশি-বিদেশি ওষুধ কোম্পানি গড়ে উঠতে থাকে, যেগুলোর অধিকাংশেরই কারখানা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতা অর্জন করে, তখন আমাদের ওষুধশিল্পের অবস্থা ছিল খুবই দুর্বল। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন সাহায্যের সঙ্গে ওষুধও আসে, কিন্তু সেগুলোর একটা বড় অংশ স্থানীয় স্বাস্থ্য চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ না হওয়ায় তেমন কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়নি। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ‘সাহায্যের ওষুধ’ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ‘প্রয়োজনীয় ওষুধের তালিকা’ প্রস্তুত করার জন্য অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের নেতৃত্বে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়।
সদ্য স্বাধীন দেশের নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব ছিল, তারই প্রতিফলন হিসেবে ১৯৭৩ সালের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের স্থানীয় উৎপাদন এবং প্রাপ্যতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সে সময়েই ওষুধসংক্রান্ত আইনগুলোর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও আলোচিত হয়। ১৯৭৫–এর ১৫ আগস্টের হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ডে দেশ হারায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, সেই সঙ্গে স্বাধীন দেশে ওষুধনীতি প্রণয়নের প্রথম উদ্যোগটি ভ্রূণ অবস্থায় ধ্বংস হয়ে যায়।
পরবর্তী সময়ে ১৯৭৯ সালে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ওষুধসংক্রান্ত আইনগুলো সংশোধন করে একটা যুক্তিসংগত কঠোর ওষুধনীতির খসড়া প্রণয়ন করে। ওষুধ উৎপাদকদের বাধার ফলে সেই প্রস্তাবিত ওষুধনীতি বাস্তবায়িত তো হয়ইনি, এমনকি নীতি প্রণয়ণের উদ্যোক্তা মন্ত্রীকে অপসারিত হতে হয়। ঠিক সে সময় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী গণমানুষের জন্য ন্যায়সংগত মূল্যে, মানসম্মত অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিক্যালস প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে ডা. জাফরুল্লাহ মূলত ওষুধের রাজনৈতিক অর্থনীতি তথা ওষুধ খাতের অভ্যন্তরীণ রহস্যঘেরা জগৎ বিশেষত ওষুধের গবেষণা খরচের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন, উৎপাদন খরচ সম্পর্কে অস্পষ্টতা এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ট্রান্সফার প্রাইসিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার চেষ্টা করেন।
১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক শাসন জারি করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেন। সামরিক শাসক এরশাদ জনমানসে তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য কিছু জনবান্ধব উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা করেন। তারই অংশ হিসেবে জাতীয় ওষুধনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে তিনি আট সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেন। জেনারেল এরশাদ চাতুর্যের সঙ্গে তাঁর এই উদ্যোগকে গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামকে কমিটির সভাপতির দায়িত্ব দেন। এই কমিটির অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন দেশের স্বনামধন্য অধ্যাপক, ওষুধবিজ্ঞানী, চিকিৎসক এবং ঔষধ প্রশাসনের কর্মকর্তা। এই কমিটিতে ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর অন্তর্ভুক্তি ছিল একটি দিকবদলকারী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, যার মধ্য দিয়ে নীতি প্রণয়নের অভিমুখ গণমুখী হয়ে ওঠে। প্রথম সভায় বিশেষজ্ঞ কমিটি ওষুধনীতির যে লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করে, সেগুলো ছিল ঝুঁকিপূর্ণ, অনিরাপদ, সন্দেহজনক কার্যকারিতা, অপ্রয়োজনীয় ও মিশ্রণজাত ওষুধগুলো বাজার থেকে পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা, ওষুধ খাতে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য জাতীয় ওষুধশিল্পের সক্ষমতা বাড়ানো এবং নিরাপদ ও মানসম্মত ওষুধের ন্যায়সংগত মূল্যে প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
সে সময় দেশে নিবন্ধিত ওষুধ কোম্পানির সংখ্যা ছিল ১৬৬ অথচ দেশের ১৮২ কোটি টাকার ওষুধ বাজারের ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত মাত্র আটটি বহুজাতিক কোম্পানি। প্রস্তাবিত ওষুধনীতিতে দেশীয় ওষুধশিল্পের বিকাশের ওপর গুরুত্ব প্রদান করায় বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর দূতাবাস তৎকালীন সামরিক সরকারের ওপর কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করে। প্রবল আন্তর্জাতিক চাপ এবং মন্ত্রিসভায় বহুজাতিকদের পক্ষের সদস্যদের পরামর্শ উপেক্ষা করে জেনারেল এরশাদ তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মেজর জেনারেল এম শামসুল হক কর্তৃক উপস্থাপিত বিশেষজ্ঞ কমিটির প্রস্তাবিত ‘জাতীয় ওষুধনীতি ১৯৮২’–এর সব সুপারিশ গ্রহণ করে ‘ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮২’–এ স্বাক্ষর করার মাধ্যমে সেটিকে আইনে পরিণত করেন।
জাতীয় ওষুধনীতি ১৯৮২ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে তখন বাজারে থাকা ৪ হাজার ৩৪০টি ওষুধের মধ্যে তিন ধাপে পর্যায়ক্রমে ১ হাজার ৭৪২টি ওষুধ নিষিদ্ধ বা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়। মানুষের কাছে ওষুধ সহজলভ্য করা তথা ওষুধ খাতে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশীয় ওষুধশিল্পের বিকাশের উদ্দেশ্যে কিছু কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। যেহেতু সহজ প্রযুক্তির ওষুধের বাজার ছিল বড় এবং তা দেশীয় কোম্পানিগুলোর সামর্থ্যের মধ্যে, সেগুলোর উৎপাদনের একচেটিয়া সুযোগ দেওয়া হয় দেশীয়দের। ফলে দেশীয় কোম্পানিগুলোর বাজারে অংশীদারত্ব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রযুক্তিগত সামর্থ্যও বাড়তে শুরু করে। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে উচ্চপ্রযুক্তির ওষুধ উৎপাদনে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু তারা সহজ ও অন্যায্য মুনাফার সুযোগ সংকুচিত হওয়ায় এই নীতির তীব্র বিরোধিতা শুরু করে এবং কয়েকটি সংবাদপত্রও বহুজাতিকদের পাশে দাঁড়িয়ে এই নীতির বিরোধিতা করে। আরও দুঃখজনক সত্য হলো যে বেশ কিছু দেশীয় বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ চিকিৎসকও বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব ও ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ বিবেচনায় এই নীতির বিরোধিতা করেন।
সরকার প্রাথমিক বিরোধিতার বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর ১৯৮৭ সালে ওষুধের মূল্য নির্ধারণের নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির অন্য তিনজন সদস্য ছিলেন সালমান এফ রহমান, ড. হুমায়ুন কে এম এ হাই এবং ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। কমিটি উৎপাদনের জটিলতার মাত্রা বিবেচনা করে ওষুধের কাঁচামাল ও প্যাকেজিং সামগ্রীর ট্যাক্সসহ মূল্যের ওপর পাঁচ ধরনের (৫০ থেকে ২২৫ শতাংশ) মার্কআপ প্রস্তাব করে। এই নীতিমালা অনুসরণ করেই ১৯৮৭ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বাজারের সব ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যার ফলে ওষুধের বাজারে অনৈতিক মুনাফার সুযোগ কমে যায় এবং বাজারের অন্যান্য পণ্যের তুলনায় ওষুধের দামও দীর্ঘদিন স্থিতিশীল থাকে বলে সাধারণ মানুষের কাছে ওষুধ অন্যান্য পণ্যের চেয়ে তুলনামূলক বেশি ক্রয়সাধ্য থাকে। লক্ষণীয় যে এই নিয়ন্ত্রিত মূল্যের সময়েই দেশীয় কোম্পানিগুলোর বিকাশ ঘটে, তবে অনৈতিক মুনাফার সুযোগ কমে যাওয়ার কারণে কয়েকটি বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে।
তীব্র গণ–আন্দোলনের ফলে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে একটি মহল থেকে প্রচারণা শুরু হয় যে এই ওষুধনীতি বিনিয়োগবান্ধব নয়। ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের অবস্থান থেকে সরে আসার ফলে পর্যায়ক্রমে ওষুধের পেছনে মানুষের ব্যয় বাড়তে থাকে।
২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় ওষুধনীতি বিনিয়োগবান্ধব উদারীকরণের যে সিদ্ধান্তগুলো ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলোর নীতিগত বৈধতা দেওয়ার লক্ষ্যেই প্রণীত হয়, যদিও তখনো আইন হিসেবে ওষুধ (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৮২ বলবৎ ছিল। জাতীয় ওষুধনীতি ২০০৫ প্রণয়নের ঘোষিত উদ্দেশ্যগুলো ছিল প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে তাল মেলানো, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে ওষুধ খাতের সামর্থ্য বাড়ানো এবং মানসম্মত ওষুধের রপ্তানিকারক হিসেবে দেশকে সক্ষম করে তোলা। স্পষ্টতই এই নীতি প্রধানত ওষুধশিল্পের বিকাশের উদ্দেশ্যে প্রণীত। উল্লেখ্য, ‘জাতীয় ওষুধনীতি ২০০৫’–এ মন্ত্রণালয়ের নাম ছাড়া আর কোথাও ‘স্বাস্থ্য’ শব্দটিরও উল্লেখ ছিল না।
উল্লিখিত সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী সময়ে ২০১৬ সালে নীতিপ্রণেতারা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ‘জাতীয় ওষুধনীতি ২০০৫’–এর মূল সুর অক্ষুণ্ন রেখেই সেটির পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করেন। ফলে ‘জাতীয় ওষুধনীতি ২০১৬’ দেশীয় ওষুধশিল্পের অধিকতর বিকাশের জন্য উপযোগী হলেও মানুষের ওষুধের প্রাপ্যতার প্রধান নিয়ামক মূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পূর্বতন উদার নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে। এমনকি এই নীতিতেও কাঁচামাল উৎপাদনের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতার ফলে দেশের ওষুধ খাত ‘জাতীয় ওষুধ নীতি ১৯৮২’ প্রবর্তনের ৪০ বছর পরও কাঁচামালের ক্ষেত্রে প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানিনির্ভর রয়ে গেছে। এ ছাড়া আগামী ২০২৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে মেধাস্বত্ব ছাড়ের সুবিধাটি শেষ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির বিষয়টিও নীতিতে প্রয়োগযোগ্য মাত্রায় প্রতিফলিত হয়নি।
বর্তমানে বাজারে প্রায় ১ হাজার ৩৫০টি জেনেরিক ওষুধ ৩৫ হাজার ট্রেড নামে বাজারে পাওয়া যায়, অথচ রাষ্ট্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগারের বার্ষিক সক্ষমতা মাত্র ৫ হাজার। ১৯৯২ সালে বাজারের সব ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের যে আইনি ক্ষমতা সরকারের ছিল, সেটি নিজেই সংকুচিত করে মাত্র ১১৭টিতে নামিয়ে আনল। বিগত ৩১ বছরে ওষুধের সংখ্যা ৩৫০ থেকে বেড়ে ১ হাজার ৩৫০ হলেও মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতাধীন ওষুধের সংখ্যা একটিও বাড়েনি। সাধারণ মানুষের কাছে মানসম্মত ওষুধ সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ওষুধের মান নিয়ন্ত্রণের সক্ষমতা এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতা বৃদ্ধি করার কোনো কার্যকর ও দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই। তবে এই নীতির ফলেই বাংলাদেশের ওষুধশিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ হয়েছে এবং চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ওষুধই দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পৃথিবীর ১৫০টির বেশি দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে, যার বাজারমূল্য প্রায় ১৮৮ মিলিয়ন ডলার।
পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের ওষুধশিল্পের বর্তমান বিকাশ, সাফল্য ও প্রসারতার ভিত্তি হচ্ছে ‘জাতীয় ওষুধ নীতি ১৯৮২’। কিন্তু আমরা জানি যে ‘ওষুধ’ স্বাস্থ্য অর্জন, রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় একটি উপাদান, আর তাই ওষুধশিল্পের এই অভূতপূর্ব বিকাশ প্রধানত স্বাস্থ্য রক্ষায় অবদান রাখার মাধ্যমেই অনূদিত হওয়ার কথা ছিল। জাতীয় ওষুধনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র তার সব নাগরিকের কাছে অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে পারলেই সেটা হয়ে উঠতে পারত বাংলাদেশের কল্যাণমুখী রূপান্তরের অন্যতম প্রারম্ভিক পদক্ষেপ।
অধ্যাপক মো. সায়েদুর রহমান: চেয়ারম্যান, ফার্মাকোলজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), ঢাকা